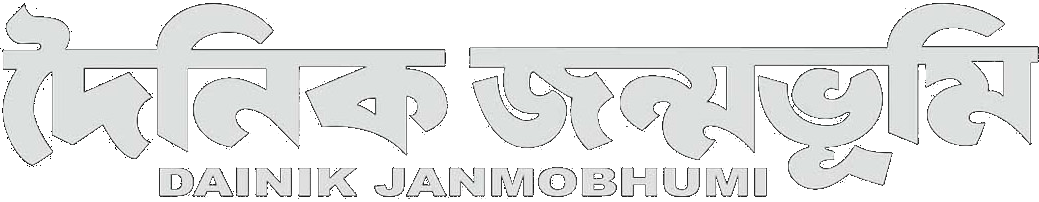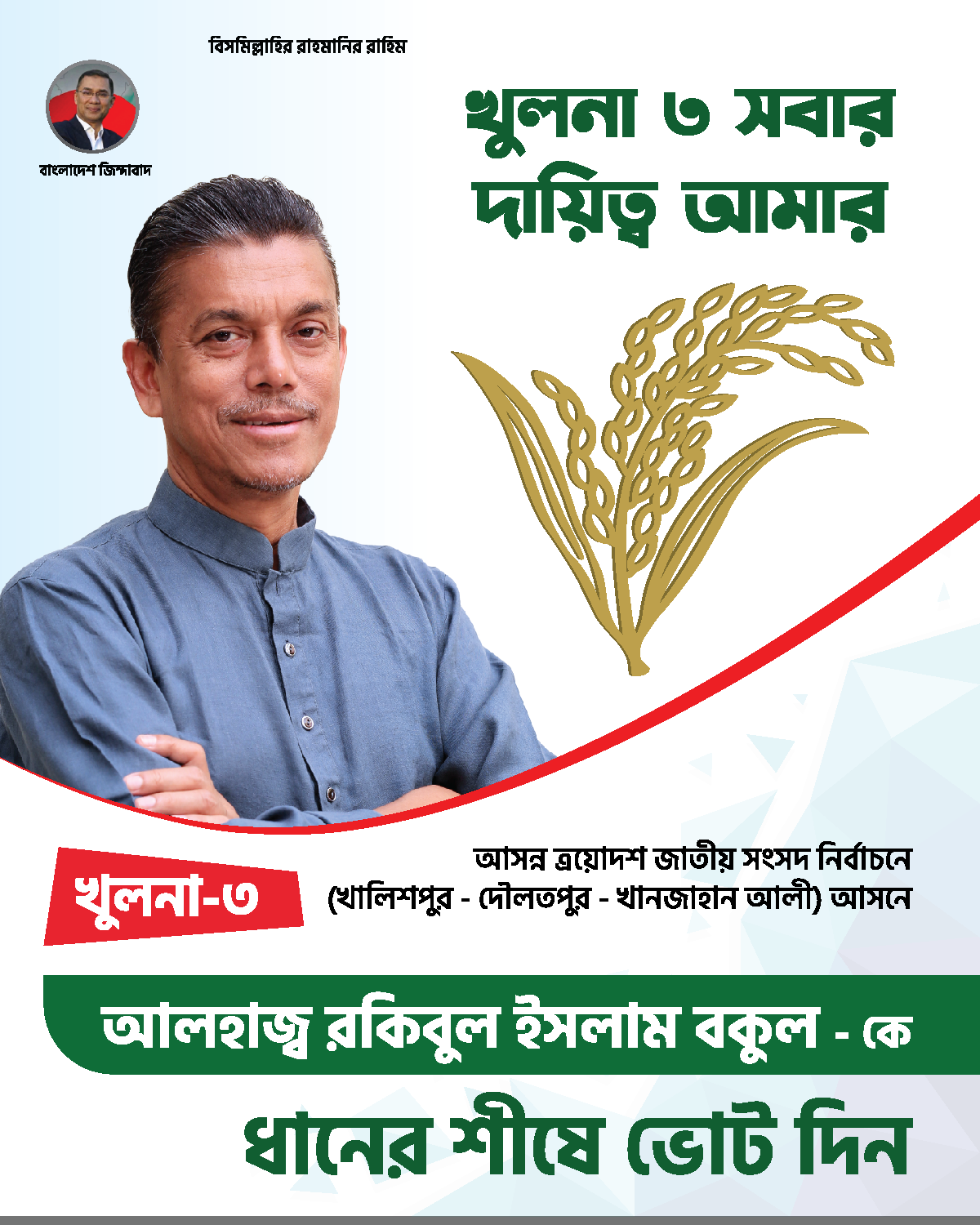সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : শারদীয় দুর্গাপূজার আজ বিজয়া দশমী। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পাঁচ দিনব্যাপী এই শারদ উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি বছর। আজ মঙ্গলবার বিসর্জনের দিন সকালে হবে দশমীর বিহিত পূজা। পূজা শেষে দর্পণ ও বিসর্জন। শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী উপলক্ষে আজ সরকারি ছুটির দিন।
গতকাল সোমবার মহানবমীতে মন্দির, মণ্ডপে যেন মিলেমিশে গেছে আনন্দ-বেদনা। দেবীর বন্দনায় ছিল ভিন্ন এক আবহ। পূজার উদ্যাপন আর দেবীকে বিদায়ের সুর বেজেছে ভক্তের হৃদয়ে। সকালে কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজার মাধ্যমে শুরু হয় নবমীর আনুষ্ঠানিকতা। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন। ভক্তদের হৃদয়ে মগ্নতা আনতেই যেন এল দুপুরের হঠাৎ বৃষ্টি। রাজধানীর মণ্ডপগুলোতে বিকেলের আগপর্যন্ত নবমীর উৎসব ছিল শান্তলয়ের।
ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন শহর থেকে এসেছিলেন অনেকে। তাঁরা রাজধানীর প্রতিমা দেখতে এসেছেন। বিকেল চারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মণ্ডপে প্রতিমার কাছে বসেছিলেন চট্টগ্রামের সুভাষ চক্রবর্তী। লাল রঙের প্রাধান্য দিয়ে সাজানো দেবীকে সাক্ষী রেখে ভক্তদের হাতে চরণামৃত দিচ্ছিলেন তিনি। কারও কপালে দিলেন যজ্ঞের কালির ফোঁটা। জানালেন, মন্দিরের পুরোহিতের আত্মীয় তিনি। বৃষ্টির পানিতে জগন্নাথ হলের পুকুরটা ভরে উঠেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে যেমন চলছিল দলেবলে ছবি তোলা, আবার কেউ কেউ একা বসেছিলেন ঘাটের লাল সিঁড়িতে।
কাছেই রমনা কালীমন্দিরের প্রবেশপথের দুই পাশ থেকে শুরু হয়েছে আলোকসজ্জা। বড় নিম আর মেঘশিরীষগাছেদের গায়েও লেগেছে রঙিন বাতি।
ফুচকা, চটপটি, গোলগাপ্পার দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ধূপকাঠি, সিঁদুর, আলতার দোকানগুলো।
প্রবেশপথে দেখা গেল বড় গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রবীণ। মোটা কাচের চশমা চোখে ফোকলা মুখে হাসি দিচ্ছেন ঢাকার নবাবগঞ্জ থেকে আসা শুকলাল মণ্ডল। নাতনি মিতু সরকার তাঁর ছবি তুলে দিচ্ছেন। শুকলাল মণ্ডল নিজের বয়স ৭০ বললেও, মিতু বললেন ঠাকুরদার বয়স আরও বেশি। মনঃক্ষুণ্ন হয়েই যেন গটগট করে মণ্ডপের দিকে হাঁটা শুরু করলেন শুকলাল। তাঁর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল, ভেতরের মাইকের রবীন্দ্রসংগীত বাইরে আসছে না। এ মন্দিরে প্রতিমার পেছনের আবহে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সবুজ রং। সন্ধ্যার মুখে শুরু হলো এখানে ঢাকের বাদ্য। বাগেরহাটের মোল্লাহাট থেকে এখানে এসেছেন এক দল ঢাকবাদক। তাঁদের মধ্যে আছেন সানাই এবং বাঁশিবাদকও। তারক বিশ্বাস সানাইয়ের সুর তুলছিলেন প্রতিমার সামনে বসে। তখন সারি সারি মানুষ ভক্তিভরে দর্শন করছেন দেবীর। ফার্মগেট থেকে আসা দীপাঞ্জলি পোদ্দার আর ওয়ারীর তুষার কান্তির মতো অনেক ভক্ত তখন প্রণাম করছেন দেবীকে।
রমনা কালীমন্দিরের দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন এক বছর পর হয় বলে জানালেন পুরোহিত মধুসূদন চক্রবর্তী। তিনি বললেন, দয়াগঞ্জের শিবগঞ্জ, ঢাকেশ্বরী এবং রমনা কালীমন্দিরের প্রতিমার বিসর্জন দশমীতে হয় না। এক বছর পর হয়। বিজয়া দশমীতে হয় ঘট বিসর্জন। সাতটি করে ঘট স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে দেবী দুর্গার জন্য স্থাপিত প্রধান ঘটটি ছাড়া বাকি ছয়টির বিসর্জন হবে দশমীতে।
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের মণ্ডপটি এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নান্দনিক সজ্জার জন্য। বাদামি রঙের প্রাধান্য দিয়ে ছিমছামভাবে সাজানো হয়েছে। বৃষ্টির জন্য বিকেল পর্যন্ত মানুষ কম থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে এ মণ্ডপে এসেছেন অনেকে।
বৃষ্টিবাদলা মাথায় নিয়েও ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে যথেষ্ট ভিড় ছিল গতকাল সারা দিনই। ভক্তরা বললেন, মাকে বিদায় জানাতে হবে বলে বেদনা আছে। একই রকম ভিড় ছিল রামকৃষ্ণ মিশনেও। রাত ১০টার দিকে নামে ভক্ত–দর্শনার্থীর ঢল। মিশনের স্বামী শান্তিকরানন্দ মহারাজ প্রথম আলোকে জানালেন, ভিড় আছে, উৎসব আছে, তবু দেবীকে বিদায়ের রাগিণী বেজে উঠেছে ভক্তদের মনে।
এ বছর সারা দেশে ৩২ হাজারের বেশি পূজামণ্ডপ হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতে মণ্ডপ হয়েছে প্রায় ২৫০টি। আজ বিজয়া দশমীতে সকালে দর্পণ বিসর্জনের পর থেকে শুরু হবে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি। রাজধানীর অধিকাংশ মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন হবে বুড়িগঙ্গায়।
বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দেবী মহামায়াকে বিশ্বপ্রকৃতিকে, আদ্যাশক্তি দেবী যোগমায়াকে ব্রহ্মের শক্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ব্রহ্ম তার শক্তি বলেই সগুণ হন এবং সগুণ হলে তিনি সৃষ্টিকার্যে ব্রতী হন। এই ব্রহ্মই সগুণ হয়ে পালন করেন এবং ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। ব্রহ্ম যে রূপে সৃষ্টি করেন, তার নাম ব্রহ্মা; তিনি যে রূপে পালন করেন, তার নাম বিষ্ণু এবং যে রূপে ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন, তার নাম শিব। এক থেকে তিন আবার তিনে মিলে এক।
আবার ব্রহ্ম যখন সৃষ্টিকার্যে ব্রতী হন, পালন করেন এবং ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন, তখন এক কথায় তাকে ‘ঈশ^র’ বলা হয়। ‘ঈশ^র’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু। ঈশ^র সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়ের প্রভু। আবার ঈশ^র যখন ভক্তকে কৃপা করেন, তখন তাকে বলা হয় ভগবান। সুতরাং ঈশ^র বা ভগবান আলাদা কেউ নন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। এক ভিন্ন দুই নেইÑ ‘একমেবাদ্বিতীয়ম’। তাই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী বহু ঈশ্বররবাদী নয়। তাহলে অবতার বা দেবদেবীরা কারা? তারাও পূজনীয়। এ কথা ঠিক। কিন্তু অবতার বা দেবদেবীরা ঈশ^র নন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য ব্রহ্ম যুগে যুগে কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্ম রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বলে তাকে বলে অবতার।
আবার ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের এক-একটি শক্তি বা গুণের প্রতীক বা প্রকাশক হলেন একেকজন দেব বা দেবী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবদেবীরা ঈশ্বর নন ঈশ্বরের এক-একটি গুণ বা শক্তির প্রতীক। যেমন ‘দেবী দুর্গা’। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। আদ্যাশক্তি মহামায়া বা যোগমায়ার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। এ শক্তি ন্যায় ও সত্যেরও প্রতীক। তিনি অন্যায় ও অসত্যকে ধ্বংস করে ন্যায় ও সত্যের প্রকাশ ঘটান।
একবার মহিষাসুর নামে এক অসুর স্বর্গ ও মর্ত্য (পৃথিবী) দখল করে নিয়েছিল। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল স্বর্গরাজ্য থেকে। আর দেবতাদের উপায়ও ছিল না। দেবতা ব্রহ্মা মহিষাসুরকে এই বর দিয়েছিলেন যে, কোনো পুরুষ মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না। মহিষাসুর মনে করল যে, সে কার্যত অমর বরই লাভ করেছে। কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না তার ধারণায় কোনো নারী এত শক্তি ধরে না যে, সে মহিষাসুরের মতো এত বড় বীরকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু এই বরের মধ্যে একটা ফাঁক ছিল। কোনো পুরুষ মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না কোনো নারী বধ করতে পারবে না, এমন বর তো দেওয়া হয়নি। অতঃপর সব দেবতার সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হলো। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি থেকে আবির্ভূত হলেন দেবী দুর্গা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ফিরে পেলেন তার স্বর্গরাজ্য। স্বর্গে ও পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এলো। এ বিজয় থেকেই হলো বিজয়োৎসব। এরই নাম বিজয়া।
আবার ত্রেতা যুগে লঙ্কার রাজা রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল রামের পত্নি সীতা দেবীকে। রাবণকে পরাজিত করে শ্রী রামচন্দ্র পালন করেন বিজয় উৎসব। এ থেকেও পালিত হয় বিজয়া। মহিষাসুরকে বধ করতে দেবীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল চার দিন। তিথির হিসেবে তিথিগুলো ছিল আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এ শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয় হয়েছিল। এ জন্য এ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিকেই বলা হয় বিজয়া দশমী। দুর্গাপূজার চার দিনের দিন দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বিজয়া দশমী পালন করা হয়।
দেবী দুর্গা তো অমর। তাহলে তার আবার বিসর্জন কী? হিন্দু শাস্ত্র মতে, দেবীকে পূজার জন্য আহ্বান করে এলে মাটির প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূজা শেষ হলে দেবীকে বলা হয়, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। তখন প্রতিমা থেকে তাকে মুক্ত করা হয়। তখন ওই মাটির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। সুতরাং বিসর্জন নামে দেবী বা কোনো দেবের ধ্বংস নয়, যে মাটির প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, সেখান থেকে মুক্ত করে, তাকে যথা ইচ্ছা চলে যেতে বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দেওয়া হয় না। দেব বা দেবীর প্রতিমা গৃহেই থাকে। পরবর্তী পূজার আগে (বছরান্তে) পুরাতন প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কাঠের প্রতিমা হলেও তা নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবর্তন করা হয়। ধাতব কিংবা প্রস্তরের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। সেই স্থলে নিত্য পূজা করা হয়।
সুতরাং বিজয়া দশমীর তাৎপর্য হচ্ছে দুটি একটি দেবী দুর্গার বিজয়। অপরটি শ্রী রামচন্দ্রের বিজয়। রামচন্দ্র অকালে দেবী দুর্গার পূজা করে ছিলেন। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা বাল্মীকির রামায়ণে নেই। তবে অন্য কবিদের রচিত রামায়ণে এবং পুরাণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা রয়েছে। দেবীর নিদ্রাকালে রাম তাকে জাগ্রত করেছিলেন বলে শরৎকালের দুর্গাপূজায় ‘বোধন’ নামক দেবীর জাগরণের একটি অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু বসন্তকালের দুর্গাপূজায় এ বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। তবে কেবল রামচন্দ্রই যে শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন তা নয়, শরৎকালে দুর্গাপূজার রীতি অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল।
বিজয়া দশমীর আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। হিমালয় রাজকন্যা দেবী দুর্গা বা পার্বতী বা উমা নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন দেবতা শিবকে। শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বত। সেখান থেকে দেবী দুর্গা বা পার্বতী পিতৃগৃহে আসেন। আশি^ন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন পিত্রালয়ে থাকার পর দশমী তিথিতে পতিগৃহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেন। কন্যাকে বিদায় জানানোর বেদনায় বিধুর হয়, বিষাদাচ্ছন্ন হয় দশমী তিথি। তাই দশমী তিথি বিষাদের বেদনার।
বাঙালি হিন্দুবাড়িতে বিবাহিত কন্যারাও বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে চলে যান। এ ক্ষেত্রে দেবী দুর্গার বিদায় বেদনা ও কন্যার বিদায় বেদনা এক হয়ে যায়। বাঙালি হিন্দুরা মনে করেন, বিজয়া দশমীতে তারা কেবল দেবী দুর্গাকে বিদায় দিচ্ছেন না, যেন নিজের কন্যাকে বিদায় দিচ্ছেন। এভাবে দেবী হয়ে ওঠেন ঘরের মেয়ে যে নাইওরে এসে, তিন দিন থেকে চার দিনের দিন স্বামীগৃহে ফিরে যান। এভাবে পূজাপার্বণের মধ্যে বাঙালির সমাজ ও যাপিত জীবনের প্রতিফলনও ঘটে। বিজয়া দশমী এমনই একটি ধর্মীয় কৃত্য যার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের একটি দিকের প্রতিচ্ছায়া উপলব্ধি করা যায়।
কথাটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য সহজবোধ্য। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে দেবী কৈলাস পাড়ি দেন। সেই কারণেই ‘বিজয়া দশমী’ নাম। কিন্তু এই দশমীকে ‘বিজয়া’ বলা হয় কেন, তার পৌরাণিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে একাধিক কাহিনি সামনে আসে।
দুর্গা পূজার অন্ত চিহ্নিত হয় বিজয়া দশমীর মাধ্যমে। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, এই দিনেই পিতৃ-আবাস ছেড়ে দেবী পাড়ি দেন স্বামীগৃহ কৈলাসের দিকে। এই দিনেই তাই দেবীর প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। ভারত ও নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দিনটি নানাভাবে পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই দিনটিকে ‘বিজয়া দশমী’ বলা হয় কেন? কোন ‘বিজয়’-কেই বা চিহ্নিত করে দিনটি?
বিজয়া‘দশমী’ কথাটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য সহজবোধ্য। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে দেবী কৈলাস পাড়ি দেন। সেই কারণেই ‘বিজয়া দশমী’ নাম। কিন্তু এই দশমীকে ‘বিজয়া’ বলা হয় কেন, তার পৌরাণিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে একাধিক কাহিনি সামনে আসে। পুরাণে মহিষাসুর-বধ সংক্রান্ত কাহিনিতে বলা হয়েছে, মহিষাসুরের সঙ্গে ৯ দিন ৯ রাত্রি যুদ্ধ করার পরে দশম দিনে তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন দেবী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনি অনুসারে, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে দেবী আবির্ভূতা হন, এবং শুক্লা দশমীতে মহিষাসুর-বধ করেন। বিজয়া দশমী সেই বিজয়কেই চিহ্নিত করে।
তবে উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দিনে যে দশেরা উদযাপিত হয়, তার তাৎপর্য অন্য। ‘দশেরা’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ‘দশহর’ থেকে, যা দশানন রাবণের মৃত্যুকে সূচিত করে। বাল্মীকি রামায়ণে কথিত আছে যে, আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতেই রাবণ-বধ করেছিলেন রাম। কালিদাসের রঘুবংশ, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, কিংবা কেশবদাসের রামচন্দ্রিকা-য় এই সূত্রের সঙ্গে সংযোগ রেখেই বলা হয়েছে, রাবণ-বধের পরে আশ্বিন মাসের ৩০ তম দিনে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করেন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ। রাবণ-বধ ও রামচন্দ্রের এই প্রত্যাবর্তন উপলক্ষেই যথাক্রমে দশেরা ও দীপাবলি পালন করা হয়ে থাকে। আবার মহাভারতে কথিত হয়েছে, দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের শেষে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমীতেই পাণ্ডবরা শমীবৃক্ষে লুক্কায়িত তাঁদের অস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন এবং ছদ্মবেশ-মুক্ত হয়ে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ঘোষণা করেন। এই উল্লেখও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য বৃদ্ধি করে।
দশেরা ও বিজয়া দশমী দিনটি কেবল হিন্দুদের কাছেই নয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কথিত আছে সম্রাট অশোক এই বিশেষ দিনটিতেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পুরান অনুযায়ী আবার দশেরার দিন রাবণ বধের পর এক নতুন সূচনা হয়ে থাকে। এর পরই বর্ষাকাল বিদায় নিয়ে শীতের শুরু হয়ে যায়।
দশমী তিথিতে দেবী আবার পাড়ি দেবেন কৈলাসে। এই দিনেই মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় এবং শুরু হয় আবার এক বছরের অপেক্ষার পালা। ‘দশমী’ মানেই ঘরের মেয়ে অর্থাৎ উমার বিদায় বেলা। পিতৃগৃহ ছেড়ে উমা এবার ফিরে যাবেন কৈলাসে স্বামী মহাদেবের কাছে। তাই মর্ত্যবাসীর মন খারাপ। দুর্গাপূজার এই শেষদিনটিকে দশমী বা বিজয়া দশমী বলা হয়ে থাকে। কেন দশমীকে বিজয়া দশমী বলা হয়, তা এখন জেনে নেব আমরা।
মহিষাসুর নামে এক অসুর ব্রহ্মার বর পেয়ে প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল দখল করে নেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করেন। ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছিলেন, কোনো পুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না। তবে কোনো নারী তাকে বধ করতে পারবে না এমন বর দেওয়া হয়নি। তখন সব দেবতার সম্মিলিত শক্তি থেকে আবির্ভূত হলেন দেবী দুর্গা। পুরাণে মহিষাসুর বধের কাহিনি অনুসারে টানা নয় দিন ও নয় রাত যুদ্ধের পর শুক্লা দশমীতে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। এই বিজয় লাভকেই বিজয়া দশমী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ত্রেতা যুগে লংকার রাজা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। দেবী দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে রাম স্ত্রীকে উদ্ধার করতে লংকা আক্রমণ করেন। শুক্লা দশমীতেই তিনি রাবণকে বধ করেন। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামের জয়লাভকেও চিহ্নিত করে বিজয়া দশমী। উত্তর ও মধ্য ভারতে এই দিনে দশেরা উদযাপিত হয়। তবে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। ‘দশেরা’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ ‘দশহর’ থেকে, যার অর্থ দশানন রাবণের মৃত্যু। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে, আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতেই লঙ্কেশ্বর রাবণকে বধ করেছিলেন রাম। কালিদাসের রঘুবংশ তুলসীদাস রামচরিত মানস সূত্রের সঙ্গে সংযোগ রেখেই বলা হয়েছে, রাবণ বধের পরে আশ্বিন মাসের ৩০তম দিনে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করেন রাম, সীতা, লক্ষণ। রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথাক্রমে দশেরা ও দীপাবলি পালন করা হয়ে থাকে। দশেরা অর্থাৎ নবরাত্রি, এর প্রথম নয় দিন মা দুর্গাকে পূজা করা হয় নানাভাবে। নবরাত্রি মানে নয়টি রাত্রি, যা নয়টি গ্রহের পরিচালনায় ঠিকমতো চালিত করতে পারে। শুধু দুর্গাপূজার বাহ্যিক আড়ম্বরই নয়, অন্তর থেকে দেবীকে পূজা করে প্রতিটি গ্রহের প্রভাবে যেন ঠিকভাবে শরীর চালিত হয়, সেই প্রার্থনা করা। বিজয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে জ্ঞানার্জন। এই শুভদিনে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ, উঁচু-নীচু বিচার না করে সবাই একাত্মবোধে আবদ্ধ হয়। সব ক্ষুদ্রতা ও পাশবিক বৃত্তির অবসান ঘটিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের ভাবনা জাগ্রত করে মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়ার সাধনাই হচ্ছে মায়ের বিজয়া দশমীর বিসর্জন পর্ব। দশমীর সকালে এক কৌটা সিঁদুর নিয়ে মায়ের মন্দিরে যাওয়া এবং সেই সিঁদুর থেকে কিছুটা মায়ের চরণে অর্পণ করা, বাকিটা বাড়ি নিয়ে চলে আসা। সেই সিঁদুর সারা বছর পুরুষ, নারী নির্বিশেষে ব্যবহার করে বিপদ দূর করার শক্তি হিসাবে। বিজয়া দশমীর দিন সকালে রাম মন্দিরে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো। দশমী পূজার অঞ্জলি দেওয়ার সময় সাদা বা নীল অপরাজিতা ফুল অর্পণ করা। শক্তির আরাধনা চলতে থাকে। অতঃপর দশম দিনে মাকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। তারপর মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। ‘আসছে বছর আবার এসো’-এই বলে তাকে আবাহন জানানো হয়। শুরু হয় সব বিভেদ ভুলে একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে মিষ্টিমুখ করা। বিজয়া দশমীতে আমাদের প্রার্থনা-সবাই যেন একসঙ্গে শান্তি, সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করতে পারি।