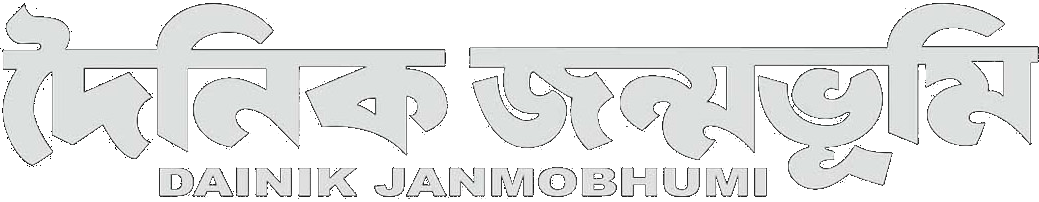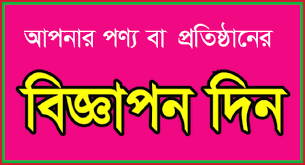সিরাজুল ইসলাম শ্যামনগর : আধুনিকায়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী। পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু। কোনো এলাকা বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের গড় আবহাওয়াই হচ্ছে জলবায়ু। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা নামে অধিক পরিচিত। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে ‘গ্রিনহাউস প্রভাব’ বলা হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনের শুধু একটি কারণ নয়, অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ বিষাক্ত গ্যাসের নিঃসরণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ, গ্রিনহাউস গ্যাস ও মানব সৃজিত কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেশদূষণ। যেমন- পারমাণবিক বিস্ফোরণ, শিল্পকারখানার বর্জ্য, কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, বেশি বেশি ফসল পাওয়ার জন্য জমিতে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ গাছ কেটে সবুজ ধ্বংস অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পকারখানা স্থাপন, ইটের ভাটা, জ্বালানি ইত্যাদি।
পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। যার ফলে জ্ঞান ও মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণে প্রতিবছর নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবহাওয়ার মৌসুমি ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণে বিশ্বের যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ।
আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (CRI) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এই সমীক্ষা চালানো হয় ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৯৩টি দেশের ওপর।
উল্লেখ্য, ওই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৭ এবং ২০০৮ সালের প্রতিবেদনেও বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষতিগ্রস্তের বিচারে বিশ্বব্যাপী গবেষকরা বাংলাদেশকে পোস্টার চাইল্ড (Poster Child) হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।
গবেষনায় বলা হয়, বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। আর উপকূলীয় এলাকায় এখন যে ৪৩ লাখ মানুষ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার, তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটিতে।
জলবায়ু গবেষক ড. আহসান চৌধুরী বলেন, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্সে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে আছে ঠিকই, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলা করার মতো সক্ষমতা নেই। তবে আমরা আন্তর্জাতিক ফোরামে জোর দাবি তুলতে পারি। কারণ, কার্বন নিঃসরণে আমাদের ভূমিকা একেবারে নগণ্য। এ জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলো। তারা এর ক্ষতিপূরণ দেবে বলেও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেনি।
তিনি বলেন, আশঙ্কা করা হচ্ছে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২ কোটি মানুষ বাড়িঘর হারাবে ২০৫০ সালের মধ্যে। এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বন্যাপ্রবণ এলাকায় দেখা যায়, প্রতিবছরই নদীভাঙনে শত শত বাড়িঘর বিলীন হয়ে যায়। এরাই তো বাস্তুচ্যুত। এ বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক তহবিল দরকার। আবার আমাদের সরকারের জলবায়ু অভিযোজনে অগ্রাধিকার প্রকল্প নিতে হবে। এ জন্য আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকতে হবে।
ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ কেন্দ্রের গবেষক ড. এহতেশামুল কবির বলেন, বিশ্বব্যাপী জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে মানুষেরই ভুলের কারণে। এটা আসলে প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা নয়। এ জন্য বাস্তুচ্যুতদের অধিকার আদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কাছে জোর দাবি জানাতে হবে আন্তর্জাতিক ফোরামে। এখন সময় এসেছে, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রটোকল থাকা উচিত।
আবহমান কাল থেকে এ দেশে ঋতুবৈচিত্র্য বর্তমান ছিল, ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে এ দেশে উপলব্ধ হয়; গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত- বসন্ত -এই ছয় ঋতুর কারণে দেশটিকে ষড়ঋতুর দেশও বলা হয়ে থাকে। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হয়। মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল চলে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ দেশে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকে, তাই জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলে বর্ষা মৌসুম। এ সময় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অনেক সময়ই বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। এ ছাড়াও মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের আগমুহূর্তে কিংবা বিদায়ের পরপরই স্থলভাগে ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কিংবা সাগরে নিম্নচাপ, জল-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, যার আঘাতে বাংলাদেশ প্রায় নিয়মিতই আক্রান্ত হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে এখন দেশের ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্যই পাল্টে যাচ্ছে।
২০০০ সনে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে কক্সবাজার উপকূলে বছরে ৭.৮ মিমি. হারে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। গত চার দশকে ভোলা দ্বীপের প্রায় তিন হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২১০০ সাল নাগাদ সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মি. উঁচু হতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৮.৩ অংশ নিমজ্জিত হতে পারে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূত্রমতে, রাজশাহীর উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯১ সনে পানির স্তর ছিল ৪৮ ফুট, ২০০০ সনে তা নেমে ৬২ ফুট এবং ২০০৭ সালে তা নেমে যায় ৯৩.৩৪ ফুটে। স্বাভাবিক বন্যায় দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যার সংখ্যা ও তীব্রতা দুটিই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন সিডর আক্রমণ করার মাত্র দুই বছরের মধ্যে শক্তিশালী সাইক্লোন নার্গিস ও আইলা এবং ২০১৩ সালের মে মাসে মহাসেন (আংশিক) আঘাত হেনে কৃষিকে বিপর্যস্ত করে তোলে।
তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমের রোগের আক্রমণ বাড়বে। বাংলাদেশে বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। ধান গাছের কচি থেকে ফুল ফোটার সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি হলে এবং অতি নিম্ন তাপে (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে) শিষে ধানের সংখ্যা কমে যেতে পারে। ফুল ফোটা বা পরাগায়নের সময় যদি অতি উষ্ণ তাপ থাকে তাহলে চিটার সংখ্যা থোড় অবস্থার চেয়ে বেশি হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার কারণে ধান গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধান গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়।
১৮৫০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ৫০ বছরের প্রতি দশকে তাপমাত্রা বেড়েছে ০.১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গত ১০০ বছরের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণ। গত ২০১২ সালে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বিংশ শতাব্দীর চেয়ে ০.৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।
সম্প্রতি ‘নাসা’ একটি ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ করেছে। গত ৪০ বছরের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার এমান্ডসন সাগরের কাছে থাকা কিছু গ্লেসিয়ার (বরফের সিট) এমনভাবে গলে গেছে যে, তা আর কোনোভাবেই বরফ হয়ে ফিরে আসবে না। ওই গ্লেসিয়ার যদি সম্পূর্ণ গলে যায়, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১.২ মিটার বেড়ে যাবে। আর যদি পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার সমস্ত বরফ গলে যায়, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৩.৫ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যাবে। পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার পাশাপাশি পূর্ব অ্যান্টার্কটিকাতেও বরফ ক্ষয়ের একই প্রবণতা লক্ষ্ করা যাচ্ছে।
গ্রিনল্যান্ডের বরফের চূড়ার ক্ষয় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আরও ভয়াবহ অশনি সংকেত দিচ্ছে। যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আগাম ধারণা আগামী দুই-তিন দশকেই আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে চীন ও বাংলাদেশ ভয়াবহ বিপদে পড়বে বলে নাসা সতর্ক করে দিয়েছে।
সাইক্লোন সিডরে সাড়ে ৩৪ লাখ মানুষের বাড়িঘর ভেসে গিয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালে ওই ধরনের সাইক্লোনে তিন মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস হবে। এতে ৯৭ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। ২০৮০ সাল নাগাদ সমুদ্রস্তর ৬৫ সেন্টিমিটার উঁচু হলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ৪০ শতাংশ উৎপাদনশীল ভূমি হারাবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় দুই কোটি মানুষ খাবার পানিতে লবণাক্ততার সমস্যার মুখে পড়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনে বন্যার ঝুঁকিও বাড়বে। বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।
২০১৬ সালে ৭ নভেম্বর মরক্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলন। এটা ছিল ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের ৫৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা। ১২০টি দেশের মন্ত্রী বা মন্ত্রপর্যায়ের প্রতিনিধিরিাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট খরা, বন্যা ও ঝড়-বৃষ্টির কারণে বাস্তচ্যুত জনগণের ক্ষতি ও সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের উল্লেখ করে বলেন, ‘ওই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল। এখন ওই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় ওই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করার সময়। শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বকে আরও নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিন্ত স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সমান অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানান, জলবায়ু চুক্তিতে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারির। ’
সম্মেলনের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা শুরু হওয়ার আগে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন তার বক্তব্যে ধনী দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের প্রতিশ্রুত এক হাজার কোটি ডলার দ্রুত পরিশোধের আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো ওই তহবিলের সাহায্য নিয়ে যাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর কাজ করতে পারে- এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
মারাকাশে ১২ দিনব্যাপী ২২তম জলবায়ু সম্মেলনে আলোচনায় আশাব্যঞ্জক কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে সমালোচনা করেছে বিশ্বের অধিকাংশ জলবায়ুবিষয়ক আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন।
বিশ্বে সকল ভারী কারখানা ও যান্ত্রিক যানবাহন যে কার্বন নিঃসরণ করে, তার শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে উন্নত ও ধনী দেশগুলোর দ্বারা। কিন্তু বিশ্বের সব রাষ্ট্রই তার দ্বারা আক্রান্ত। নিঃসরিত কার্বন বায়ু প্রবাহের দ্বারা সব দেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কাজেই কার্বন নিঃসরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর সাহায্যে ধনী দেশগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে, প্যারিস সম্মেলনে ধনী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনো পুরোপুরি রক্ষিত হচ্ছে না।
জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হচ্ছে অসহায় দরিদ্র মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে নারী, শিশু ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ও শিশু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবং এই পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। এই অবস্থায় করণীয়ই বা কী হবে, সে সম্পর্কেও তারা ওয়াকিবহাল নয়। তাই জলবায়ু সম্পর্কে নারী ও শিশুসহ বাংলাদেশের মানুষকে ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং কাজ করতে হবে।