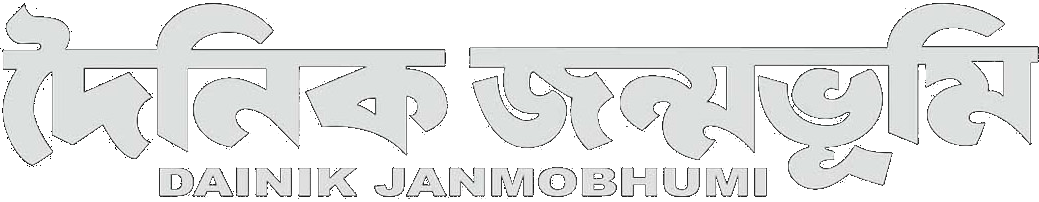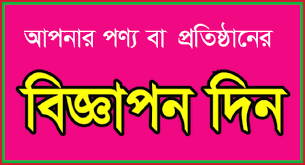সিরাজুল ইসলাম, শ্যামনগর: সিডি, ভিসিডি ও ডিভিডি প্লেয়ার। শব্দগুলোই যেন হারিয়ে গেছে! তথ্য-প্রযুক্তির নিত্যনতুন উপহার একঘরে করে দিয়েছে এক সময়ের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সিডি, ভিসিডি ও ডিভিডি প্লেয়ারকে।
এসব যন্ত্রের ব্যবহার এখন একেবারেই শূন্যের কোঠায়। উপযোগিতা হারিয়ে যন্ত্রগুলো এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। অথচ দেড় যুগ আগেও ঘরে ঘরে ছিল এগুলোর ব্যাপক চাহিদা। শহর-গ্রাম সবখানেই ছিল ইলেকট্রনিক্স এসব যন্ত্রের দাপট।
নব্বই দশকে বাংলাদেশে ভিসিডি, ডিভিডি ও এমপি থ্রি সিডি প্লেয়ারের প্রচলন শুরু হয়। শুরুর দিকে শহর কেন্দ্রিক প্রচলন হলেও পরবর্তীতে সহজলভ্য হওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে গ্রামগঞ্জে। ভাড়ায় এক ঘর হতে আরেক ঘরে ঘুরত এসব যন্ত্র। তখন বাংলা সিনেমা, নাটকসহ গান দেখতে শুনতে বাসাবাড়ি থেকে হোটেল-রেস্টুরেন্ট, অফিস কক্ষ সবখানেই বিনোদন সহায়ক এসব যন্ত্রের ছিল অবাধ বিচরণ। এখন সেই প্রচলন নেই, তাই যন্ত্রগুলো হারিয়েছে সেই কদর।
তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রসরতার প্রভাবে ভিসিডি, ডিভিডি ও সিডি প্লেয়ারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ফেসবুক, ইউটিউবের আর মেমরি কার্ডের যুগ। কেউ আর মতো প্লেয়ারে গান শোনে না।
প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের হারিয়ে যাওয়া ভিসিআর, ভিসিপি, ভিসিডি, ডিভিডি ও থ্রি সিডি প্লেয়ারের আর দেখা মেলে না। যদিও কালেভদ্রে গ্রামগঞ্জে নতুবা চিত্রধারণ ও ভিডিও সম্পাদনাকারী প্রতিষ্ঠানে দুই-একটি দেখা যায়, সেগুলোও ব্যবহার হতে না হতে বিকল প্রায়। ধুলাবালু পড়ে হারিয়ে গেছে যন্ত্রগুলোর জৌলুশ।
সম্প্রতি নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রামে এক বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখা মেলে ইলেকট্রনিক্স এই যন্ত্রের। একঘরে একটি চেয়ারের ওপর ধুলাবালুতে বদলে গেছে যন্ত্রটির চেহারা। সঙ্গে পড়ে রয়েছে পুরোনো দিনের হিন্দি সিনেমা আর বাংলা গানের ভিডিও কমপ্যাক্ট ডিস্ক। এখন এসব শুধুই স্মৃতি। যেন জাদুঘরে সংরক্ষণ উপযোগী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে!
প্লেয়ারটির প্রসঙ্গ তুলতে মুচকি হাসেন বাড়ির কর্তা মনজুর রহমান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক এই কর্মকর্তা বলেন, ক্যাসেট প্লেয়ারে গান শোনার যুগ শেষ হয়েছিল ডিভিডি ও এমপি থ্রি সিডি প্লেয়ার আসার পর। আর এখন গান দিন দিন হয়ে উঠছে অনলাইন কেন্দ্রিক। তাই এই যন্ত্রও উপযোগিতা হারিয়েছে।
রংপুর নগরীর ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের ব্যবসায়ী সহিদুল ইসলাম জানান, নব্বই দশকের দিকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বাড়ায় ওই সময় একচেটিয়া ব্যবসা করেছেন। ভিসিআর, ভিসিপি, ভিডিও ক্যাসেট, ডিভিডি ও এমপি থ্রি সিডি প্লেয়ার মেশিন ভাড়ায় চলত। এটাকে পুঁজি করে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে এসবই এখন স্মৃতি।
সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়তেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সন্ধ্যা নামতেই পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে জমে যায় ভিড়। সারা দিনের কর্মযজ্ঞ শেষে খানিকটা আনন্দ আর স্বস্তির আশায় মানুষ ছুটে যায় সেখানে। চায়ের চুমুকের সঙ্গে শুনতে থাকে ক্যাসেটে বাজানো হিন্দি-বাংলা গান; এতেই যেন মেলে প্রশান্তি। আবার শীতের সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে জটলা করে ব্যাটারির সাহায্যে চালিত ভিসিআরে ছবি দেখা—দৃশ্যগুলো আজ যেন রূপকথার গল্পের মতন। শহরাঞ্চলে সকালের মিষ্টি আলোয় বারান্দায় বসে সংবাদপত্র হাতে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কলের গান শোনার দৃশ্যও আজ আর নেই।
সময় চলে তার নিজ গতিতে। তার এ গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে কালের গর্ভে স্থান করে নিয়েছে কলের গান, ক্যাসেট, ভিসিআরের মতো অনেক দুর্লভ সব বিনোদন মাধ্যম। অথচ একটা সময় এগুলোই ছিল এ দেশের মানুষের বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ।
১৯২০-এর দশকে গ্রামোফোন ছিল বিনোদন লাভের অন্যতম মাধ্যম। ১৮৭৭ সালে কাঠের বাক্সে চোঙ্গা লাগানো যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন টমাস আলভা এডিসন। এর নাম দেন ফনোগ্রাম। ১৮৮৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী বার্নিলার টিনফয়েল এ যন্ত্রটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে নাম দেন গ্রামোফোন। বাংলার সঙ্গে এ যন্ত্রের পরিচয় ঘটান এফডব্লিউ গেইসবার্গ। তিনি ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রথম রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার।
শহর-গ্রাম সবখানেই যন্ত্রটি ছিল সমান জনপ্রিয়। সেসময়ে বনেদি পরিবারে গ্রামোফোন না থাকাটা অনেকটা বিস্ময়কর ছিল। এটি ছিল তাদের আভিজাত্যের প্রতীক। তাছাড়া গ্রামের নানা উৎসবে গান বাজানোর জন্য এ গ্রামোফোনই ব্যবহার করা হতো। লতা মুঙ্গেশকরের ‘পেহলি মুলাকাত’ কিংবা ‘ছাইয়া দেনার’ মতো হিন্দি গানসহ বাংলা-উর্দু গানও বাজানো হতো। ষাট থেকে সত্তরের দশকেও এ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল।
বাঙালির গান শোনার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সত্তরের দশকে ক্যাসেটের আবির্ভাব ছিল সংগীতের নতুন সংযোজন। বলা যায়, ১৯৮০-এর দশকটি রাজত্ব করেছে ক্যাসেট। ১৯৬৩ সালে প্রথম ক্যাসেট চালু হয়। ক্যাসেটকে কমপ্যাক্ট ক্যাসেট বা শুধু টেপও বলা হতো।
যদিও এ যন্ত্র তৈরির ইতিহাসটি একটু পুরনো। ১৮৮৫-৮৬ সালের দিকে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তার ভোলটা ল্যাবরেটরিতে আদি যুগের টেপ রেকর্ডার তৈরি করেছিলেন। পরে প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৫ সালে ম্যাগনেটোফোন আবিষ্কার করা হয়। মূলত আধুনিক কম্প্যাক্ট ক্যাসেট বাজারে নিয়ে আসে ফিলিপস কোম্পানি ১৯৬৩ সালে।
ক্যাসেটের ভেতরে লম্বা সরু সেলুলয়েডের ফিতা থাকত। এ ক্যাসেট দিয়ে গান রেকর্ড এবং গান বাজানো—দুটো কাজই করা যেত। একেকটি ক্যাসেট ছিল ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে সামান্য বড়। প্রথম দিকে ধনী পরিবারগুলো গান শোনার এ যন্ত্র ব্যবহার করত। পরে প্রযুক্তির কল্যাণে ছোট ছোট ক্যাসেটে বাজার ছেয়ে যায়। কি ধনী কি গরিব সর্বত্র ক্যাসেটের জয়গান। সকাল, সন্ধ্যায় এসব ক্যাসেটে বাজানো হতো মান্না দে, লতা মুঙ্গেশকর, নীনা হামিদ, আব্বাসউদ্দীনের মতো শিল্পীদের গান। কখনোবা শোনা যেত ‘আমার প্রাণের প্রাণ পাখি’ কিংবা ‘মেঘনার কূলে ঘর বান্দিলাম’ গানগুলো। আধুনিক প্রযুক্তির ভিড়ে হারিয়ে যায় ক্যাসেট।
রেডিওতে খেলার খবর শোনা আজকাল ছবির দৃশ্যে দেখা যায়। ভারত-পাকিস্তান কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের টান টান উত্তেজনাপূর্ণ খেলার ধারাভাষ্য এখন হয়তো রেডিওতে অনেকেই শোনে না। তবে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত মানুষের কাছে রেডিও ছিল গ্রহণযোগ্য একটি মাধ্যম। গান, খেলাধুলা, দেশ-বিদেশের খবর, আবহাওয়ার সংবাদ রেডিওর মাধ্যমে শুনত। আবার সপ্তাহের একটি নির্ধারিত দিনে শ্রোতাদের জন্য অনুরোধের গানের আয়োজনও করা হতো। এসব অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য সন্ধ্যার পর চায়ের দোকানে জটলা করত গ্রামের মানুষ।
রেডিও বাংলার ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সাক্ষী। ৭ মার্চের ভাষণ থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে রেডিওর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। যুদ্ধের সময় রেডিওর ভূমিকার কথা কারো অজানা নয়। রেডিওতে ভেসে আসা ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’, ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’, ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’—গানগুলো যুদ্ধাঙ্গনে সৈনিকদের মনোবলকে আরো দৃঢ় করেছিল।
ছোট্ট এ যন্ত্র এখন আর দেখা যায় না। একটা সময় কমবেশি সবার ঘরেই ছিল রেডিও। যাত্রাপথে সাইকেলের হ্যান্ডলে রেডিও ঝুলিয়ে রাখার দৃশ্যও আর নেই। কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে রেডিও নামের বাক্স। তার জায়গাটি দখল করে নেয় এফএম রেডিও।
১৯৭০-এর দশকে বাজারে আসে ভিসিআর। ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার বা ভিসিআর দিয়ে চলচ্চিত্র দেখা হতো। ব্যাটারিচালিত এ যন্ত্র চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ঘরে বসে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল ভিসিআর। যন্ত্রটির ভেতরে ক্যাসেট ঢোকালেই রেখা-অমিতাভের মুকাদ্দার কি সিকান্দার, সুচিত্রা সেনের হারানো সুর, দীপ জ্বেলে যাই, আমজাদ হোসেনের গোলাপী এখন ট্রেনে ও ছুটির ঘণ্টার মতো আরো কত শত ছবি দেখা যেত। গ্রামাঞ্চলে চাঁদা তুলে ভিসিআরে ছবি দেখার গল্প প্রায়ই প্রবীণদের কাছ থেকে শোনা যায়। কিন্তু অত্যাধুনিক যন্ত্রের ভিড়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ভিসিআর।
প্রযুক্তির দুনিয়ায় আজ যেটা নতুন কাল সেটা পুরনো। নব্বইয়ের দশকের তথ্য সংরক্ষণের একটি অন্যতম ফরম্যাট সিডি বা ডিভিডি। ভিসিআরের পরই মূলত ডিভিডির আগমন। এ প্রযুক্তিটির কারণে ভিডিওচিত্র সংরক্ষণ ও ভিডিও ছবি দেখার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। মানুষ তার পছন্দের ছবি কিংবা শিল্পীর গানের সিডি কিনত। ঘরে বসেই শুনত সেসব গান। এখন আর ডিভিডির ব্যবহার নেই। আর তথ্য সংরক্ষণের জন্যও তৈরি হয়েছে নানা বিকল্প। পেন ড্রাইভ বা এক্সটারনাল ড্রাইভ—এগুলো যেন কাজকে আরো সহজ করেছে।
আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে কানে হেডফোন লাগিয়ে চলতে চলতে গান শোনার কথা কেউ ভেবেছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু এ রকম ঘটেছিল। সনির এক বিশেষ আবিষ্কার ছিল ‘ওয়াকম্যান’। ছোট্ট এ যন্ত্রটি দীর্ঘদিন মানুষকে চলার পথে গান শোনার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ যন্ত্রটি ছিল আজকের এমপিথ্রি, এমপিফোর প্লেয়ারের মতো। যন্ত্রটি সর্বপ্রথম বাজার আসে ১৯৭৯ সালে। সেসময় যন্ত্রটির গ্রহণযোগ্যতা ছিল দারুণ। কিন্তু ২০১০ সালের পর থেকে যন্ত্রটি তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে মূল ‘ওয়াকম্যান’ হারিয়ে গেলেও এর নতুন সংস্করণ হিসেবে আমরা পেয়েছি এমপিথ্রি, ফোর, ওয়াকম্যান অ্যাপ।
পুরনো যাবে নতুন আসবে। এটাই নিয়ম। আর ঠিক এ নিয়মের হাত ধরেই এসব যন্ত্রের পরিবর্তে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, আইফোনের মতো অনুষঙ্গগুলো। হয়তো সময়ের প্রয়োজনে একদিন আধুনিক এ মাধ্যমগুলোও বিদায় নেবে। তবে পুরনো সময়ের মাধ্যমগুলো মানুষের স্মৃতিতে দাগ কেটে যাবে অনন্ত কাল ধরে।