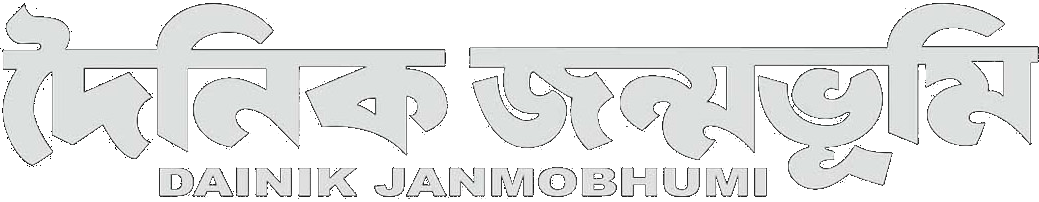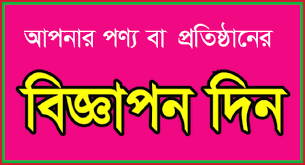বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে। চলমান অর্থনৈতিক ঘাটতির ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মূল্যস্ফীতির তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এক বছর ধরেই মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির জন্য সরকার আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্ববাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমলেও এর প্রভাব বাংলাদেশের বাজারে পড়ছে না। পত্রপত্রিকার খরব অনুযায়ী, দেশে মে মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ, যা ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে ২০১২ সালের মার্চে ১০ দশমিক ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছিল। এরপর আর কখনো ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য প্রকাশের এ সূচক দুই অঙ্কের ঘরে যায়নি। পরের মাসেই মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমে আসে।
নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ভোগ্যপণ্য তালিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেকে মূল্যস্ফীতির অঙ্ক ন্যূনতম ১৫ শতাংশের ওপরে বলছেন। গত বছর একই সময়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। তিন মাস ধরেই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রের মূল্যস্ফীতিই এ সামগ্রিক বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।
মূল্যস্ফীতি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এর সঙ্গে বেকারত্ব তৈরির ফলে স্ট্যাগফ্লেশন (একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস) অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যা অর্থনীতির জন্য আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে
প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকার গড়ে ৬ শতাংশে মূল্যস্ফীতি ধরে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজেটে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেই উল্লেখ করে এটিকে বাজেটের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখছে গবেষণা সংস্থাগুলো। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। সরকার অবশ্যই মূল্যস্ফীতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি।
সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতির এ প্রতিবেদন বেশ হতাশাজনক। এভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়ার ক্ষেত্রে অনেক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। ডাল, চিনি, তেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের মজুত সীমিত পরিমাণে রয়েছে। এর সঙ্গে ডলার-সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। সম্প্রতি আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পেঁয়াজের দাম কমে আসে। যা বাজার ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। মূল্যস্ফীতির কারণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করা প্রকৃত অর্থে যৌক্তিক নয়। অনেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবেই দেখিয়েছেন যে মূলত মূল্যস্ফীতির জন্য অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনাই দায়ী। যুদ্ধের অভিঘাতের মধ্যেই বাংলাদেশের সমপর্যায়ের দেশ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক দেশই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সফলভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।