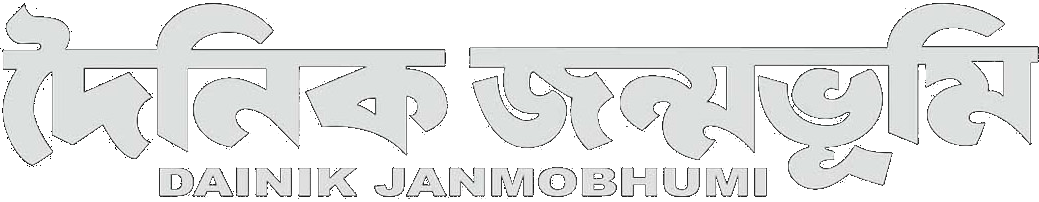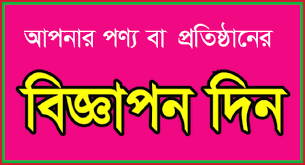সিরাজুল ইসলাম, শ্যামনগর : ২০০৯ সালের ২৫ মে আজকের দিনে সর্বনাশা আয়লা লন্ডভন্ড করে দেয় উপকূলীয় জনপদ। প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাত হানার ১৬ বছর আজ। উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আইলার ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি অনেকে।
সে দিনটির কথাও ভুলতে পারেনি কয়রা ও পাইকগাছাসহ উপকূলের মানুষ। ঝড়ে স্বজন হারানো মানুষের কান্না যেনো আজও শোনা যায়। বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সে কথা মনে করে আজও আতকে উঠেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিস্তীর্ণ জনপদ যেন লন্ডভন্ড হয়ে ধ্বংস লীলায় পরিণত হয়। কাঁদায় স্বজন হারা মানুষকে।
২১ মে ২০০৯ তারিখে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড় আইলার এবং উপকূলভাগে আঘাত হানে ২৫ মে। এর ব্যাস ছিলো প্রায় ৩০০ কিলোমিটার, যা ঘূর্ণিঝড় সিডরের থেকে ৫০ কিলোমিটার বেশি। সিডরের মতোই আইলা প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে উপকূল অতিক্রম করে, তবে পরে বাতাসের বেগ ৮০-১০০ কিলোমিটার হয়ে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি, সিডরের তুলনায় কম হয়েছে।
মালদ্বীপের আবহাওয়াবিদরা এর নাম আইলা দেন। আইলা’ শব্দের অর্থ ডলফিন বা শুশুকজাতীয় জলচর প্রাণী। ঘূর্ণিঝড় আইলা পটুয়াখালি, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আইলার প্রভাবে নিঝুম দ্বীপ এলাকার সকল পুকুরের পানিও লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৭১১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিধ্বস্থ হয়েছে।
ফলে তলিয়ে যায় খুলনার দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার ২০টি ইউনিয়ন পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভেড়িবাধ ভেঙে ও ছাপিয়ে গিয়ে লোনা পানিতে তলিয়ে যায়। ৭৬ কিলোমিটার বাঁধ পুরোপুরি এবং ৩৬২ কিলোমিটার বাঁধ আংশিকভাবে ধ্বসে পড়ে। এই দুই অঞ্চলে প্রাণ হারিয়েছে মোট ১৯৩ জন।
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, আইলায় প্রায় দুই লাখ একর কৃষিজমি নোনা পানিতে তলিয়ে যায়। আক্রান্ত এলাকাগুলোয় পানীয় জলের উৎস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ২,০০,০০০ একর কৃষিজমি লোনা পানিতে তলিয়ে যায় (৯৭ হাজার একরের আমন ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়) কাজ হারায় ৭৩,০০০ কৃষক ও কৃষি-মজুর।
আক্রান্ত এলাকাগুলোয় পানীয় জলের উৎস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। জলোচ্ছাস ও লোনা পানির প্রভাবে, গবাদি পশুর মধ্যে কমপক্ষে ৫০০০ হাজারগরু ও ২,৫০০ হাজার ছাগল মারা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের কয়েক মাস পর থেকে এলাকাগুলোয় গাছপালা মরতে শুরু করে ও বিরানভূমিতে পরিণত হয়। কমপক্ষে ৩,০০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় (২,৪৩,০০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়)। দুই লাখ ৪৩ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।
আইলা-পরবর্তী সময়ে উপকূল ভাগের মানুষের জীবনযাত্রায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। ঘূর্ণিঝড় আইলার রেশ কেটে গেলেও তার ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে দক্ষিণাঞ্চলে। অনেকে এলাকা ছাড়া হয়েছে আবার অনেকের পেশা বদলে গেছে। জীবীকার তাগিতে। সেই আইলার ক্ষত নিয়ে শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ বাসিত হয়ে শ্যামনাগর সাতক্ষীরা ও খুলনায় বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে সেখানেই বসবাস করছেন ভোটের সময় আসলে প্রার্থীরা তাদেরকে যাতায়াত- খরচ দিয়ে ভোট দিতে নিয়ে আসে এলাকায় ,,,পুকুরে মিঠা পানির বদলে নোনা পানি। ফলে পানীয় জলের সংকট নিত্যদিনের ঘটনা। আইলার পর থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে খাবার পানির সংকটে ভুগছে লক্ষ লক্ষ মানুষ,,,
নোনা জলের আগ্রাসনে জমিতে উৎপাদন কমে যায়। উপকূল এলাকায় লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ধানের বীজ সরবরাহ করছেন কৃষি অফিস। আইলার ১৬ বছর পরও বিভিন্ন বাঁধের ভাঙন মেরামত না হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছে উপকূলবাসী। সামান্য ঝড়ে জলবন্দী হয়ে পড়েছে উপকূলের মানুষ। কোনো কোনো গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কপোতাক্ষ আর খোলপেটুয়া নদীর জল।
ঝড়ের সময় শুরু হয় প্রাণ বাঁচাতে মানুষের দৌড়া-দৌড়ি, ছুটা-ছুটি। ঝড়ে কেউ হারিয়েছেন মা-বাবা, কেউ ভাই-বোন, কেউ বা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে চরম কষ্টে দিন অতিবাহিত করছেন এই প্রতিবেদক ও আইলার্স বলে হারিয়েছিলেন তার আপন চাচী ও ভাগ্নিকে এই প্রতিবেদন লেখার সময় তার চোখ দিয়ে ছল ছল করে পানি ঝরে ছিল চাচি ও ভাগ্নির জন্য। মানুষের আর্তি যেন থামছে না। ঝড়ে স্বজন হারানো মানুষের কান্না যেনো আজও শোনা যায়। বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সে কথা মনে করে আজও আতকে উঠেন।
২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে আমাদের গ্রামের সবুজ হারিয়ে গেছে। ওই সাইক্লোনে বেড়িবাঁধ ধ্বসে লবণ পানি প্রবেশ করেছিল। লবণ পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। লবণাক্ততায় গ্রামে ধান চাষ করা সম্ভব ছিল না। এলাকার মানুষ বাধ্য হয়ে ধানের জমিতে চিংড়ি চাষ শুরু করে। সাইক্লোন আমাদের এলাকার দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। আমরা এখন লবণ ভূমির বাসিন্দা।’ — কথাগুলো বলেন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার মাটিয়াভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শওকত আলী।
প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আইলার ১৬বছর আজ। ২০০৯ সালের ২৫ মে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আঘাত করেছিল বাংলাদেশের উপকূলে। এর প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলো। আইলায় উল্লেখযোগ্য প্রাণহানি না হলেও উচ্চ জলোচ্ছ্বাসে পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটেছে ব্যাপক। কৃষি জমি, চিংড়ির খামার, পুকুর, ডোবা সবকিছু লবণের বিষে আক্রান্ত হয়। ফলে জীবন জীবিকায় চরম সংকট দেখা দেয়। ১৬ বছর পরেও ওই অঞ্চলের মানুষ আইলার ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। সে কথাই বলছিলেন শওকত আলী।
৭২ বছর বয়সী কৃষক শওকত আলী সারাজীবন এলাকায় জমি চাষ করেছেন। তার বংশের অন্যান্য পুরুষেরাও ধান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ২০-৩০ বছর আগের দৃশ্যের সাথে এলাকার এখনকার দৃশ্যের মিল খুঁজে পান না তিনি। আইলার আগে এই এলাকার মাঠে মাঠে ছিল ধান। সে সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষি মজুরেরা এই এলাকায় আসতো ধান কাটতে। ধান কাটা শেষ হওয়া অবধি বহু মানুষের কাজ থাকতো এলাকায়। মাঠে এখন সেই কর্মব্যস্ততা নেই। উপার্জনের জন্য এই এলাকার মানুষদের যেতে হয় বাইরে।
শওকত আলীর কথাগুলোর সঙ্গে মাঠের দৃশ্যপট হুবহু মিলে যায়। কয়রা উপজেলার দক্ষিণে সুন্দরবন লাগোয়া ঘড়িলাল, চরামুখা এবং আংটিহারা গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, ফসলি মাঠ ফাঁকা। লবণাক্ততার কারণে এসব মাঠে এখন আর সবুজ নেই। এই কৃষি মাঠে যারা কাজ করতেন, তারা এখন জীবিকার জন্য অন্যত্র চলে গেছেন। গ্রামগুলোর গা ঘেঁষে শাকবাড়িয়া নদী। নদীর ওপারেই সুন্দরবন। কৃষি মাঠ এবং চিংড়ি খামার থেকে কর্মহীন মানুষদের মধ্যে অনেকে সুন্দরবনে জীবিকার জন্য যায়। কিন্তু সেখানেও আগের মতো উপার্জন নাই।
সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশের সুন্দরবন লাগোয়া এই এলাকায় এক সময় বিপুল পরিমাণ ধান উৎপাদন হতো। এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন ছিল ধান চাষ। কিন্তু ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপদ এলাকার অবস্থা বদলে দিয়েছে। জীবন জীবিকায় চরম সংকট দেখা দিয়েছে। কাজের সন্ধানে এলাকার মানুষ যাচ্ছে অন্যত্র। অনেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপদ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মানুষের জীবনের লড়াই আরো কঠিন করে দিয়েছে। এই এলাকার এক হাজার জনের মধ্যে থেকে ৭শ জনই বাইরে কাজে চলে গেছে।
শুধু কয়রা উপজেলায় নয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের আরো কয়েকটি উপজেলার দৃশ্যপট একই রকম। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত লাগোয়া সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা এবং আশাশুনি উপজেলার প্রাকৃতিক বিপদের প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা, দাকোপ উপজেলা এবং পাইকগাছা উপজেলার দৃশ্যপটও একই রকম। ঘূর্ণিঝড় আইলার ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হয় পরবর্তী সময়ের ঘূর্ণিঝড়গুলোর প্রভাব। বেড়িবাঁধ দুর্বল থাকার কারণে ওই এলাকাগুলো স্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। জোয়ারের পানির চাপে দুর্বল বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। এতে মানুষের বাড়িঘর এবং ফসলি ক্ষেতের ক্ষতি হয়। বারবার ক্ষতির মুখে পড়ে ওই অঞ্চলের বহু পরিবারে সংকট বেড়ে যায়। ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপদের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জীবিন জীবিকায় মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। ওই অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে — সুপেয় পানির সংকট, কৃষি সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, বসবাসের সমস্যা, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি।
নাজুক বেড়িবাঁধ এভাবে পড়ে থাকে বছরের পর বছর
দুর্যোগ সীমান্ত পাড়ি দিতে বাধ্য করে
‘আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে বারবার হেরে গিয়েছি। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার পরে আমি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভারত থেকে দেশে ফেরার পরে আমি ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাতে সব হারাই।’ বলছিলেন শ্রমজীবী ফারুক হোসেন।
ফারুক হোসেনের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের কুড়িকাহুনিয়া গ্রামে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফারুক হোসেনের জীবনকে ওলটপালট করে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে অনেকগুলো দুর্যোগের মুখে পড়েছেন তিনি। ২০০৯ সালে ফারুকের নিজের গড়ে তোলা সংসারে ধাক্কা দিয়েছিল আইলা। এতে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান। আইলায় ক্ষয়ক্ষতির পরে ফারুক হোসেন দেশ ছেড়ে পাশের দেশ ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। পরিবার নিয়ে তিনি সেখানে একটি বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তায় কাগজ কুড়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর অবস্থানের পরে নানান সমস্যা দেখা দেয়। ফারুক হোসেন আবার দেশে ফিরে আসেন। জমানো টাকা দিয়ে গ্রামে নিজের জমিতে বসবাসের ঘর তৈরি করেন। কিন্তু ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ সব সম্পত্তি হারিয়েছেন তিনি। পরিবারের সংকট আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।
ফারুক হোসেনের মতো আরো অনেক পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সংকটের কথা জানা গেছে। জীবন জীবিকার জন্য ভারতগামী পরিবারগুলোর সূত্র বলছে, ভারতের বিভিন্ন এলাকায় নিম্ন আয়ের অনেক পরিবার আছে, যারা বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক বিপদের মুখে পড়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলার পরে জীবন জীবিকার জন্য ভারত চলে গেছে। এদের মধ্যে একটি অংশ পরিবারসহ ভারত গেছে। অনেকে মৌসুম-ভিত্তিক কাজের জন্য ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসে। বৈধভাবেই তারা সেখানে কাজ করে। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এই মানুষের ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ধান কাটা, ধান রোপন, ইট বানানো, বাসাবাড়ি পরিস্কার, রাস্তায় কাগজ কুড়ানো ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত।
বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাকৃতিক বিপদের কারণে প্রতি বছর অনেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ কাজের জন্য ভারতে যায়। অনেকে দেশের বড় শহরগুলোতে কাজের জন্য যায়। ভারতে যাওয়ার কারণ হিসাবে পরিবারগুলো বলেছে, সেখানে উপার্জনের সুযোগ অনেক বেশি।
প্রাকৃতিক বিপদগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বাস্তচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৬বছরে এই উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৫ হাজার পরিবার গ্রাম ছেড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের সংকটাপন্ন অন্যান্য উপজেলার দৃশ্যপটও একই রকম।
বাস্তুচ্যুত মানুষদের ঠাঁই হয় নাজুক বেড়িবাঁধের উপরে
ধান চাষ, চিংড়ি চাষ — উভয়ই সংকটে
খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার গাতিরঘেরী গ্রামের বাসিন্দা বিজয় কৃষ্ণ সরকার, ৭৪, বলেন, ‘আমি সারাজীবন ধান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলাম। জমিতে ধানের উৎপাদন ছিল খুব ভালো। আইলার পর থেকে অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। জমিতে লবণক্ততা বেড়ে যাওয়ায় আমরা চিংড়ি চাষ শুরু করি। কিন্তু ঘন ঘন সাইক্লোনে চিংড়ি চাষও বহুমূখী সমস্যার মুখোমুখি। এখন আমাদের এলাকায় টিকে থাকা কঠিন হচ্ছে।’
একই উপজেলার গাতিরঘেরি, আংটিহারা, চরামুখা, ঘড়িলাল এবং নিকটবর্তী আরো অনেক গ্রামের অবস্থা একই। আংটিহারা গ্রামের রোজোয়ানুল করিম আগে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তিনি এলাকার ঘড়িলাল বাজারে ফারনিচারের ব্যবসা করছেন। প্রতিবেশীদের অনেকে উপার্জনের জন্য এলাকার বাইরে চলে গেছেন।
কয়রা উপজেলার ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলো সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার অধিকাংশ এলাকার মাটিতে লবণাক্ততা মিশে গেছে। ফলে উপজেলায় ১ হাজার ৩০০ হেক্টর কৃষি জমি অনাবাদী রয়েছে। নদী ভাঙনে বিলীন হয়েছে আরো ৪০০ হেক্টর কৃষিজমি। পানি ও মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় চিংড়ি ব্যবসায় লোকসান গুনতে হচ্ছে এ এলাকার চাষিদের। অনেকে বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করছেন।
কয়রা উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর এ উপজেলার নদীর পানিতে লবণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫-৬ পিপিটি পর্যন্ত লবণের মাত্রা এ এলাকার জন্য সহনীয়। অথচ গ্রীষ্মকালে তা ২৫-৩০ পিপিটি পর্যন্ত বেড়ে যায়। এ জন্য চিংড়ি চাষেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। জোয়ারের চাপে বাঁধ ভেঙে চিংড়িঘের ভেসে যায়। প্রতিবছর লোকসানের কারণে অনেকেই পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছেন।
কুড়িকাহুনিয়া গ্রামের কৃষক আবদুস সামাদ আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরে আরো অনেক প্রাকৃতিক বিপদ মোকাবিলা করেছেন। আম্ফানের পর তার জমিতে ধান চাষ বন্ধ। ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ওই এলাকা দশ মাসেরও বেশি সময় লবণ পানির তলায় ছিল। লবণাক্ততায় ওই এলাকার গাছপালা মরে গেছে। মাঠের সবুজ ঘাসও মরে গেছে। কৃষকেরা ধান চাষের মাধ্যমে এলাকায় সবুজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাটি ও পানিতে অতিরিক্ত লবনাক্ততার কারণে তা কঠিন হচ্ছে।
প্রতাপনগর ইউনিয়ন বাসিন্দারা বলেছেন, ‘ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের পরে গোটা ইউনিয়নের কৃষি জমি লবণ পানিতে ডুবেছিল। এলাকার বেড়িবাঁধ অত্যন্ত দুর্বল। জোয়ারের চাপে লবণ পানি প্রবেশ করে। এলাকার কৃষকেরা জমিতে ধান চাষ করার চেষ্টা করছে। লবনাক্ততার কারণে ধান ভালো হচ্ছে না। লবণ পানি ঠেকাতে দরকার শক্ত বেড়িবাঁধ।’
নারীদের জীবন জীবিকার লড়াই আরো কঠিন
নাছিমা বেগম (২৬), তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন সুন্দরবনের নিকটবর্তী একটি ছোট্ট ফকিরকোনা দ্বীপে বসবাস করছেন। ফকিরকোনার অবস্থান বাংলাদেশের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সুতারখালী ইউনিয়নে। কালাবগি প্রথমবার মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েন আইলার আঘাতে। পরে বিভিন্ন সময় হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলো ওই অঞ্চলের মানুষদের আরো বিপাকে ফেলে। ফকিরকোনা এক সময় ওই ইউনিয়নের কালাবগি গ্রামের একটি অংশ ছিল। ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্ফান কালাবগি গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফকিরকোনা এলাকাটিকে দ্বীপে রূপান্তর করেছে। সুতারখালী এবং নিকটবর্তী এলাকাগুলো ঘূর্ণিঝড় আইলার পরে প্রায় ৫ বছর লবণ পানির তলায় ছিল। নাছিমা বেগমের মত আরো অনেক পরিবার এতে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। অনেকে এলাকা ছেড়ে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যত্র চলে গেছেন। কিন্তু নাছিমা বেগমের মতো সব হারানো পরিবারগুলো অন্যত্র যেতে পারেনি। শিবসা নদী এবং সুন্দরবন এই পরিবারগুলোর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম।
বারবার বাড়ি হারানো মানুষদের লড়াই আরো কঠিন
ফকিরকোনা মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপে রূপান্তরিত হওয়ার পরে নাছিমা বেগমের জীবন জীবিকার লড়াই অনেক কঠিন হয়েছে। নাছিমাকে বিক্ষুব্ধ শিবসা নদী পাড় হয়ে মূল ভূ-খণ্ডে আসা-যাওয়া করতে হয়। উপার্জনের জন্য তার স্বামী সাগর সরদার অধিকাংশ সময় এলাকার বাইরে থাকে। সে কারণে নাছিমাকে পরিবারের সব কাজ করতে হয়। ফলে সব সময় ঝুঁকির মধ্যেই থাকতে হয় নাছিমাকে। শুধু নাছিমা নয়, তার মত আরো প্রায় ১০০ পরিবার ফকিরকোনা দ্বীপে বসবাস করেন। ওইসব পরিবারের নারীরা নাছিমার মতোই সংকট মোকাবিলা করছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নাছিমা বেগম এবং তার প্রতিবেশী পরিবারগুলো ফকিরকোনা দ্বীপে বসবাস করছে। দাকোপ উপজেলার ফকিরকোনা দ্বীপের মানুষেরা টিকে থাকার জন্য প্রাকৃতিক বিপদের সাথে লড়াই করছে। কিন্তু জলবায়ু সংকটের কাছে পরাজিত হয়েছে দাকোপ উপজেলার অনেক পরিবার। এই উপজেলার নলিয়ান গ্রামের ইয়াসিন হোসেন এবং সাদ্দাম হোসেন সাইক্লোন আইলার পরে জীবন জীবিকার জন্য খুলনা শহরে চলে গেছে। একই সময়ে কাচারিপাড়া গ্রামের রাকেশ মিস্ত্রী এবং হরষিদ মণ্ডল, গুনারী গ্রামের শঙ্কর সরদার এবং নলিয়ান গ্রামের আশাফুর রহমান জীবন জীবিকার জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে গেছে। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মধ্যে অনেক নারীরা এলাকায় অবস্থান করে পরিবার সামলাচ্ছেন। এই নারীরা বছরের পর বছর চরম সংকট মোকাবিলা করছে।
বাংলাদেশের ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল খুব বেশি সংকটের মুখোমুখি। ঘন ঘন সাইক্লোন এলাকাটিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা, ২০১৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ফণী এবং ঘূর্ণিঝড় বুলবুল, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্ফান, ২০২১ সালের ঘূর্ণিঝড় ইয়াস এবং আরো অনেক প্রাকৃতিক বিপদের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের মানুষেরা।
শুধু দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। সাত বছরে বাংলাদেশের ৫৮টি জেলায় জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিপর্যয়ে অন্তত ১,০৫৩ জন নিহত এবং ৯ দশমিক ৪ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিধস সহ দুর্যোগের কারণে দেশটি ৪,১২০ মিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সমস্ত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ (এসএফবি), ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশে কর্মরত ৪৫টি এনজিওর একটি সুশীল সমাজ-পরিচালিত নেটওয়ার্ক, এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এসএফবিকে গবেষণাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল।
লবণ পানির আগ্রাসনে বিপর্যস্ত গ্রাম
বাংলাদেশের উপকূলে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গত দুই দশকে বহু মানুষ বাড়িঘর স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি)-এর ‘গ্লোবাল রিপোর্ট অন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট ২০২১’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৪৪ লাখ ৪৩ হাজার ২৩০ জন মানুষ। তাদের প্রায় সবাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে উদ্বাস্তু হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামীতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সংখ্যা অনেক বাড়বে বলে আংশকা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হালনাগাদ গ্রাউন্ডসওয়েল প্রতিবেদন বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ২১ কোটির বেশি মানুষ ঘরছাড়া হতে পারে। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে রয়েছে চার কোটির বেশি মানুষ। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই ১৯ দশমিক ৯ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
২০২২ সালের মে এবং জুন মাসে বিশ্বকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে কেন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শীর্ষ সাতটি দেশের মধ্যে একটি। ওই দুই মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারী বর্ষা এবং আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্ষা বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু গত বছরের ভারী বর্ষা এবং আকস্মিক বন্যা ছিল ১২২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। মৌসুমী বৃষ্টিতে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশ পানির নিচে ফেলে দিয়েছে। এতে ৭ মিলিয়নেরও বেশি বাসিন্দা প্রভাবিত হয়েছে এবং প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস ও আইলায় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার নুরনগর ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল কৈখালী ইউনিয়নের আটটি গ্রাম রমজান নগর ইউনিয়নের ৭ গ্রাম মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের ১৮টি গ্রাম ইউনিয়নের ১৮টি গ্রাম গাবুরা ইউনিয়নের ২০ টিগ্রাম পদ্মপুকুর ইউনিয়নের ১৮টি গ্রাম আটুলিয়া ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রাম কাশিমাড়ী ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম এবং শ্যামনগর সদর ইউনিয়নের আটটি গ্রাম প্লাবিত হয়।