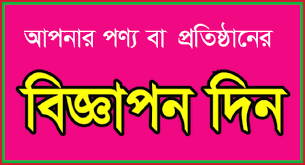সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেছেন, প্রকৃতি বদলাচ্ছে। আমাদের অবশ্যই প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উঢপকূল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হবে আর লবণাক্ততা বেড়ে ঢুকে যাবে আরও ভেতরে। মানুষ ভালো নেই, দুর্যোগ বাড়বে, এটা মোকাবিলায় প্রস্তুতিও বাড়াতে হবে। কম্যুউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নেই।
পরিবেশবাদী সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা’র (ধরা) আয়োজনে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘উপকূলের জীবন-জীবিকা : সংকট ও করণীয়’ শীর্ষক এক জাতীয় সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
আইনুন নিশাত বলেন, ষড়ঋতুর দেশে আজ চার ঋতুতে পরিণত হয়েছে। আষাঢ়েও এখন আর বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায় না। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের বিকল্প নেই। মানুষকে সচেতন হতে হবে। কম্যুউনিটি বেজড অ্যাডাপটেশন নিয়ে কাজ করতে হবে, বাড়াতে হবে কম্যুউনিটির অংশগ্রগণ।
এসময় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, নদী দখল করে প্রস্তুত করা স্থাপনাঘ
উচ্ছেদ করতে হবে। নদী দখল করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যাবে না। নদী বাঁচাতে হবে। পরিবেশ বাঁচাতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
ধরা’র সহ-আহ্বায়ক শরমীন মুরশিদ বলেন, নদী হলো পাবলিক প্রাপার্টি। এই নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে কার সিদ্ধান্ত? নদীতে বর্জ্য ফেলা আইন করে বন্ধ করতে হবে। উপকূল রক্ষায় গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। উপকূলের কম্যুউনিটির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা এমএস সিদ্দিকী বলেন, মানুষই যদি না থাকে তাহলে উন্নয়ন দিয়ে কী করবো। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচাতে হবে নদী ও পরিবেশকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঠেকাতে সবাই একত্রে কাজ করতে হবে।
সভাপতির বক্তব্যে আর্চবিশপ বিজয় নিসফরাস ডি’ক্রুজ বলেন, উপকূলের মানুষের কান্না আমরা শুনতে পাই। তাদের কান্না যেন আমাদের হৃদয়েও বাজে। সৃষ্টিকর্তার এই পৃথিবীর সব মানুষ ভাই ভাই। সংঘাতে না জড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করতে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
জাতীয় সংলাপে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আসা জলবায়ুর অভিঘাতে ভুক্তভোগীরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি, বর্জ্য থেকে পানিদূষণও ইলিশের অভয়াশ্রমের প্রবেশপথে নানান প্রকল্পে ভরাট হয়ে যাওয়ায় ভরা মৌসুমে ইলিশের দেখা না মেলার মূল কারণ। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন সমুদ্রে দীর্ঘ ডুবোচর, রাবনাবাদ, আগুনমুখা, আন্ধারমানিক এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ায় ইলিশের আনাগোনা কমে গেছে। কক্সবাজার সংলগ্ন মাতারবাড়ি অঞ্চলে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ও মৎসজীবীদের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে।
সংলাপে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুয়াকালচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান মীর মোহাম্মদ আলী এবং সরকারি সংস্থা ব্লু প্ল্যানেট ইনিশিয়েটিভের গবেষণা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপক মো. ইকবাল ফারুক
বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এক বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও জনজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি মানুষের বসবাস। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তবে উপকূলীয় অঞ্চল দেশের কৃষি, মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলেও জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিবিধ দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনপদ আজ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সূচক (২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), বুলবুল (২০১৯) এবং মোখা (২০২৩) উপকূলীয় জীবনের দুর্বলতা এবং অভিযোজন ব্যর্থতার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ৫ লক্ষাধিক প্রাণহানি, অসংখ্য পরিবার ধ্বংস ও উপকূলীয় জীবনব্যবস্থার বিপর্যয়ের স্মারক এই দিনটি আমাদের দুঃখময় স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর ‘উপকূল দিবস’ পালনের দাবি ও তাগিদটি তৈরি হয়েছে। সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষের প্রাণহানির বেদনা বহন করে চলেছে এই দিবস যা কেবল শোক পালনের জন্যই নয়, বরং এটি উপকূলের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর শক্তিকে কাজে লাগানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দুর্যোগসহনশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের দিন। আমাদের উপকূলের শক্তিকে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রে আনতে হলে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল কেবল দুর্যোগ এবং দুর্ভাগ্যের গল্প নয়, এটি শক্তি, সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধির আধার। প্রায় ১৯টি জেলার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য এবং সামুদ্রিক অর্থনীতি জাতীয় প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সমুদ্র অর্থনীতি বা ‘সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি)’। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক মৎস্য আহরণ, জাহাজ চলাচল, অফশোর সম্পদ ও পর্যটন শিল্প জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি, চিংড়ি চাষ ও লবণ উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক খাতগুলো কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। অন্যদিকে, সুন্দরবনসহ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের ‘প্রাকৃতিক ঢাল’ হিসেবে কাজ করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় এই বন শুধু মানুষকেই নয়, গোটা উপকূলকে সুরক্ষা দেয়। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক। সংগতকারণে এই অঞ্চল যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও অনন্য ভূমিকা রাখছে।
একটি টেকসই উপকূল গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন একটি সমন্বিত, মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কৌশল— যেমন: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাঁধ মজবুতকরণ, আধুনিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও টেকসই গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। টেকসই মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করা জরুরি।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মূলত মৎস্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসাভিত্তিক জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ইউএনডিপি (২০২০)-এর তথ্যানুযায়ী উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরার প্রায় ৩ কোটি মানুষ সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সকল উপকূলীয় অঞ্চলের ৭০% মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি ও মৎস্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বছরে গড়ে ৪-৫ বার তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকে। এখানকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তবে এই সম্ভাবনাময় অঞ্চল প্রতিনিয়ত একাধিক ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন এখানে জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসের প্রকোপে এখানকার জনপদ তাদের প্রাণনাশের ঝুঁকিতে থেকে হারাচ্ছে আবাসস্থল ও পরিবহন যোগাযোগব্যবস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর তথ্য (২০২০) অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,৩৮,০০০ জন নিহত হয়।
বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এক বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও জনজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি মানুষের বসবাস। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তবে উপকূলীয় অঞ্চল দেশের কৃষি, মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলেও জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিবিধ দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনপদ আজ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সূচক (২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), বুলবুল (২০১৯) এবং মোখা (২০২৩) উপকূলীয় জীবনের দুর্বলতা এবং অভিযোজন ব্যর্থতার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ৫ লক্ষাধিক প্রাণহানি, অসংখ্য পরিবার ধ্বংস ও উপকূলীয় জীবনব্যবস্থার বিপর্যয়ের স্মারক এই দিনটি আমাদের দুঃখময় স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর ‘উপকূল দিবস’ পালনের দাবি ও তাগিদটি তৈরি হয়েছে। সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষের প্রাণহানির বেদনা বহন করে চলেছে এই দিবস যা কেবল শোক পালনের জন্যই নয়, বরং এটি উপকূলের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর শক্তিকে কাজে লাগানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দুর্যোগসহনশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের দিন। আমাদের উপকূলের শক্তিকে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রে আনতে হলে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল কেবল দুর্যোগ এবং দুর্ভাগ্যের গল্প নয়, এটি শক্তি, সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধির আধার। প্রায় ১৯টি জেলার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য এবং সামুদ্রিক অর্থনীতি জাতীয় প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সমুদ্র অর্থনীতি বা ‘সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি)’। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক মৎস্য আহরণ, জাহাজ চলাচল, অফশোর সম্পদ ও পর্যটন শিল্প জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি, চিংড়ি চাষ ও লবণ উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক খাতগুলো কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। অন্যদিকে, সুন্দরবনসহ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের ‘প্রাকৃতিক ঢাল’ হিসেবে কাজ করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় এই বন শুধু মানুষকেই নয়, গোটা উপকূলকে সুরক্ষা দেয়। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক। সংগতকারণে এই অঞ্চল যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও অনন্য ভূমিকা রাখছে।
একটি টেকসই উপকূল গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন একটি সমন্বিত, মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কৌশল— যেমন: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাঁধ মজবুতকরণ, আধুনিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও টেকসই গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। টেকসই মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করা জরুরি।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মূলত মৎস্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসাভিত্তিক জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ইউএনডিপি (২০২০)-এর তথ্যানুযায়ী উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরার প্রায় ৩ কোটি মানুষ সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সকল উপকূলীয় অঞ্চলের ৭০% মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি ও মৎস্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বছরে গড়ে ৪-৫ বার তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকে। এখানকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তবে এই সম্ভাবনাময় অঞ্চল প্রতিনিয়ত একাধিক ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন এখানে জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসের প্রকোপে এখানকার জনপদ তাদের প্রাণনাশের ঝুঁকিতে থেকে হারাচ্ছে আবাসস্থল ও পরিবহন যোগাযোগব্যবস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর তথ্য (২০২০) অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,৩৮,০০০ জন নিহত হয়।
বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এক বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও জনজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি মানুষের বসবাস। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তবে উপকূলীয় অঞ্চল দেশের কৃষি, মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলেও জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিবিধ দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনপদ আজ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সূচক (২০১৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), বুলবুল (২০১৯) এবং মোখা (২০২৩) উপকূলীয় জীবনের দুর্বলতা এবং অভিযোজন ব্যর্থতার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ৫ লক্ষাধিক প্রাণহানি, অসংখ্য পরিবার ধ্বংস ও উপকূলীয় জীবনব্যবস্থার বিপর্যয়ের স্মারক এই দিনটি আমাদের দুঃখময় স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর ‘উপকূল দিবস’ পালনের দাবি ও তাগিদটি তৈরি হয়েছে। সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষের প্রাণহানির বেদনা বহন করে চলেছে এই দিবস যা কেবল শোক পালনের জন্যই নয়, বরং এটি উপকূলের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর শক্তিকে কাজে লাগানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দুর্যোগসহনশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের দিন। আমাদের উপকূলের শক্তিকে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রে আনতে হলে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল কেবল দুর্যোগ এবং দুর্ভাগ্যের গল্প নয়, এটি শক্তি, সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধির আধার। প্রায় ১৯টি জেলার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য এবং সামুদ্রিক অর্থনীতি জাতীয় প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সমুদ্র অর্থনীতি বা ‘সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি)’। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক মৎস্য আহরণ, জাহাজ চলাচল, অফশোর সম্পদ ও পর্যটন শিল্প জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি, চিংড়ি চাষ ও লবণ উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক খাতগুলো কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। অন্যদিকে, সুন্দরবনসহ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের ‘প্রাকৃতিক ঢাল’ হিসেবে কাজ করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় এই বন শুধু মানুষকেই নয়, গোটা উপকূলকে সুরক্ষা দেয়। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক। সংগতকারণে এই অঞ্চল যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও অনন্য ভূমিকা রাখছে।
একটি টেকসই উপকূল গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন একটি সমন্বিত, মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কৌশল— যেমন: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাঁধ মজবুতকরণ, আধুনিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও টেকসই গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। টেকসই মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করা জরুরি।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মূলত মৎস্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসাভিত্তিক জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ইউএনডিপি (২০২০)-এর তথ্যানুযায়ী উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরার প্রায় ৩ কোটি মানুষ সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সকল উপকূলীয় অঞ্চলের ৭০% মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি ও মৎস্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বছরে গড়ে ৪-৫ বার তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকে। এখানকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তবে এই সম্ভাবনাময় অঞ্চল প্রতিনিয়ত একাধিক ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন এখানে জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসের প্রকোপে এখানকার জনপদ তাদের প্রাণনাশের ঝুঁকিতে থেকে হারাচ্ছে আবাসস্থল ও পরিবহন যোগাযোগব্যবস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর তথ্য (২০২০) অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,৩৮,০০০ জন নিহত হয়।
প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন কিংবা ১৯৯১ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল, সেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিডর, আইলা, ফণী, আম্পান বা মোখার মতো প্রচ- ক্ষমতাশালী ঝড়গুলোতেও আমরা মৃত্যুর সংখ্যাকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। এই বৈপ্লবিক সাফল্যের পেছনে নিঃসন্দেহে রয়েছে আমাদের সময়োপযোগী আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণহানি দিন দিন কমিয়ে আনছি।
উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ, উন্নত আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক (বিশেষ করে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বা সিপিডি) একযোগে কাজ করে। ঝড়ের কয়েকদিন আগে থেকেই বিপদ সংকেত পৌঁছে যায় উপকূলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মাইকিং, রেডিও, টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারণার ফলে মানুষ দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এই সক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু, সাফল্য কি আমাদেরকে এক ধরনের আত্মতুষ্টির বিভ্রান্তিতে ভোগাচ্ছে? আমরা কি ধরে নিচ্ছি যে, মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে আনার বার্তা দিতে পারাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত সফলতা? সময় এসেছে এই প্রশ্নগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করার। সতর্কবার্তা জীবন বাঁচায়, কিন্তু সেই জীবনকে সচল রাখার জন্য যে জীবিকা প্রয়োজন, তা কি আমরা রক্ষা করতে পারছি?
বাস্তবতা হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ হলো সতর্কবার্তা, শেষ ধাপ নয়। যখন একজন উপকূলীয় বাসিন্দাকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের কথা জানিয়ে ঘর ছাড়তে বলা হয়, তখন আমরা কি ভেবে দেখেছি, তার গন্তব্য কোথায়? সংকেত পাওয়ার পর সেই মানুষটির যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত, মানসম্মত ও নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র কি আমরা আদৌ নিশ্চিত করতে পেরেছি? কাগজে-কলমে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা হয়তো বেড়েছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তব অবস্থা ভয়াবহ। বেশিরভাগ আশ্রয়কেন্দ্রই সারাবছর অবহেলায় পড়ে থাকে। দুর্যোগের সময় সেগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানি বা পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে না। বিশেষ করে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই পরিবেশ অত্যন্ত অনিরাপদ ও অবমাননাকর।
এর চেয়েও বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, গবাদি পশুর জন্য স্থানের অভাব। উপকূলীয় অঞ্চলের একটি পরিবারের কাছে তার কয়েকটি ছাগল, হাঁস-মুরগি বা একটি গরু কেবল পশু নয়, এগুলো তার জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং বছরের সঞ্চয়। যখন আশ্রয়কেন্দ্রে এই নিরীহ প্রাণীগুলোর জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকে না, তখন অনেক পরিবারই তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড়ের মধ্যে নিজেদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে, আমাদের সতর্কবার্তা ব্যবস্থা সচল থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী অবকাঠামোর কারণে পুরোপুরি কার্যকর হতে পারে না। মানুষকে কেবল ‘যাও’ বলাই যথেষ্ট নয়, তাদের একটি নিরাপদ ও মানবিক আশ্রয় নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্।
সতর্কবার্তা মানুষকে সাময়িকভাবে নিরাপদ স্থানে সরাতে পারে, কিন্তু দুর্যোগের মূল আঘাতটি আসে আমাদের ভঙ্গুর অবকাঠামোর ওপর। আর এই অবকাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উপকূলীয় বেড়িবাঁধ। জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কাতেই যখন এই বাঁধগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তখনই প্রকৃত বিপর্যয় শুরু হয়। একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসে, কেন প্রতি বছর একই জায়গায় বাঁধ ভাঙে? কেন বর্ষার আগে বা দুর্যোগের ঠিক আগমুহূর্তে জরুরি মেরামত বা আপৎকালীন সংস্কার করতে হয়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সংস্কৃতিতে। আমাদের বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে ত্রাণবান্ধব। অর্থাৎ, এমনভাবে দুর্বল করে বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়, যা ভেঙে গেলে নতুন করে ত্রাণ ও মেরামতের সুযোগ তৈরি হয়। টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাঁধ নির্মাণে যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন, সেখানে দুর্নীতি ও অবহেলার অভিযোগ প্রকট। যখন একটি পাঁচ বা ছয় ফুট জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কাতেও বাঁধ ভেঙে যায়, তখন বুঝতে হবে এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। এই দুর্বল অবকাঠামোগত ব্যর্থতা দুর্যোগের ক্ষতিকে কেবল বহুগুণ বাড়িয়েই তোলে না, এটি সতর্কবার্তার সাফল্যকেও ম্লান করে দেয়।
বাঁধ ভাঙার তাৎক্ষণিক প্রভাব হলো ঘরবাড়ি প্লাবিত হওয়া। কিন্তু, এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আরও ভয়াবহ এবং স্থায়ী। বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে যখন সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে, তা এক অপূরণীয় বিপর্যয়ের সূচনা করে। এই লবণাক্ত পানি বছরের পর বছর কৃষি জমিকে অনুর্বর করে রাখে। কৃষকের সোনালি ধানের স্বপ্ন নোনা পানিতে ডুবে যায়। মিঠা পানির মাছের ঘেরগুলো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়। সুপেয় পানির একমাত্র উৎস যে পুকুর, তা লবণাক্ত হয়ে পড়ায় তীব্র পানি সংকট দেখা দেয়। এই দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয় থেকে মানুষ সহজে ঘুরে দাঁড়াতে পারে না।