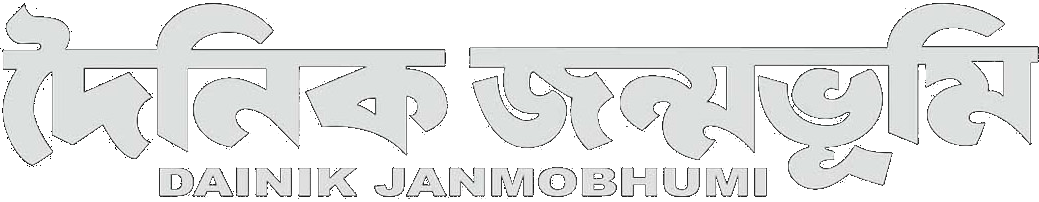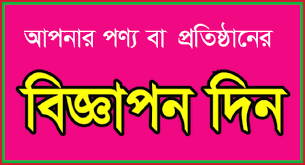ইয়াসীন আরাফাত রুমী
শুকনো মৌসুমের শুরুতেই খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের উপকুলীয় এলাকায়। এ পানি সংকট উপকূলের জনপদে প্রথমে তীব্র আকার ধারণ করলেও এখন খুলনা নগরীতেও পানির জন্য দীর্ঘ লাইন দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ইতোমধ্যে উপকূলের জনপদের পানির উৎস্য পুকুরগুলোয় পর্যাপ্ত পানি না থাকায় লোকজনের দুর্দশার অন্ত নেই। দূর দূরান্ত থেকে মাইলের পর মাইল পার হয়ে প্রতিদিন শত শত নারী পুরুষদের খাবার পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সুপেয় পানির অভাবে বাড়ছে পানি বাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা।
অপর দিকে মহানগরী খুলনার গভীর নলকূপগুলোতে এখন পানি উঠছে না। অধিকাংশ নলকূপগুলোর পানির স্তর নেমে গেছে। শরীরের সকল শক্তি ব্যয় করে এক কলস পানি নিতে হয়। অনেক নলকূপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে যেগুলো ভালো আছে সেগুলোর উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ লাইন দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।
টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল চাপতে চাপতে ঘাম ঝড়ে যায় তবু পানি উঠে না। পানির জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়।
পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েলেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আক্ষেপ করে এভাবেই কথাগুলো বলেন খুলনা মহানগরীর গগনবাবু রোডের বাসিন্দা আবু মুসা।
মহানগরীর আলী ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন বলেন, মার্চ মাসের শুরু থেকেই সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় পানি পাই না। মাঝে মধ্যে বাসার লোকজন পানির অভাবে গোসলও করতে পারেন না।
বাইতিপাড়া এলাকার বাসিন্দা হরে কৃষ্ণ বলেন, গরম শুরুর পর থেকেই হস্তচালিত নলকূপে আগের মতো পানি উঠছে না। রাতে অথবা ভোরে সামান্য পানি ওঠে। পানি নিয়ে সীমাহীন কষ্টে আছি। যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে।
ভুক্তভোগী নগরবাসীরা জানান, বাসাবাড়িতে খাবার পানি নেই, রান্নার পানি নেই, নেই গোসলের পানি। পানির জন্য অনেকেরই প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। ওয়াসার পানি নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয়। এ পানি পান করা যায় না। এতোদিন নলকূপের পানি পান করেছি। এখন নলকূপে পানি উঠছে না। প্রতিবেশীদের নলকূপ (সাবমার্সিবল পাম্প) থেকে পানি আনতে হচ্ছে। কিন্তু সাবমার্সিবল পাম্পে পানি উঠাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হওয়ায় অনেকে পানি দিতে চান না। বৃষ্টি না হলে পানির স্তর আরও নিচে নামবে এবং তাতে নগরীর ৯০ শতাংশ নলকূপ দিয়ে পানি না ওঠার পরিস্থিতি তৈরি হবে।
আক্ষেপ করে অনেকে বলেন, অধিকাংশ এলাকায় পাইপলাইনে মধুমতি নদীর পরিশোধিত পানি সরবরাহ করছে খুলনা ওয়াসা। কিন্তু সে পানি খাওয়ার যোগ্য নয়। ওয়াসা নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও খাবার পানির কষ্ট আগের মতোই থেকে গেছে।
খুলনা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, মহানগরীর ৩৮ হাজার বাড়িতে ওয়াসা পাইপলাইনে পানি দিচ্ছে। গ্রীষ্ম এলেই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক এলাকার নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়াসার নিজস্ব নলকূপেও পানি উত্তোলনের পরিমাণ কমেছে। এতে পানির জন্য নগরবাসীকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
এদিকে নগরী ছাড়াও সুপেয় পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। শহর থেকে গ্রাম সবখানেই রয়েছে সুপেয় পানির সঙ্কট। পুকুর ও জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় জেলার বিভিন্ন গ্রামে পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এতে চৈত্রের খরতাপে হাঁপিয়ে উঠছে মানুষ ও প্রাণীকূল। বিশুদ্ধ পানির অভাবে ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে দাকোপ, বটিয়াঘাটা, কয়রা ও পাইকগাছায়। এসব এলাকার অগভীর নলকূপগুলো অধিকাংশই অকেজো। যে কয়েকটি সচল রয়েছে সেগুলোর পানি লবণাক্ত ও আর্সেনিকে ভরা। যার কারণে খাবার পানি আনতে দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে যেতে হচ্ছে নারীদের।
ভুক্তভোগীরা পানির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বলে জানান। পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহে জেলা পরিষদের পুকুর/দীঘি ও জলাশয় পুনঃখনন/সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।
তবে পানির অভাবে চৈত্রের কাঠফাটা রোদে মাঠ, ঘাট, পথ, খাল, বিল ও প্রান্তর ফেটে চৌচির। দিনভর সূর্যতাপে নুইয়ে পড়ছে গাছের পাতাও। নেতিয়ে পড়েছে সবজি। ফসলি ক্ষেত বৃষ্টির অভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। সেচের অভাবে বাদামী রং ধারণ করছে ইরি ধানক্ষেত। দাকোপ, বটিয়াঘাটার মহাসঙ্কটে পড়েছেন তরমুজ চাষিরা।
এছাড়া খুলনার বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, রূপসা ও দিঘলিয়া উপজেলায় পানির স্তর নেমে যাওয়ায় এসব এলাকায় কৃষিকাজে পর্যাপ্ত পানি প্রায়া যাওয়া যাচ্ছে না। বটিয়াঘার তরমুজসব খরিপ ফসলের মাঠগুলো এখন টৌচির হয়ে যাচ্ছে। সহসা বড়ধরনের বৃষ্পিাতের সম্ভাবনা না থাকায় দ্রæত পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে।
সরজমিনে খুলনা জেলার কয়রা, বটিয়াঘাটা ও দাকোপ, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলো ঘুরে পানির সংকট চোখে পড়ে। পানির সংগ্রহের জন্য ৭/৮ কিলোমিটারেরও বেশি পথ পায়ে হাঁটতে হয়। এভাবে পানি সংগ্রহ করতে দেখা যায় শিশু এমনকি বৃদ্ধদেরও। সূত্র বলছে, জলবায়ু পরিবর্তন এই এলাকায় লবণাক্ততা বাড়িয়েছে। আইলার আগে এই এলাকায় এতটা পানির সংকট ছিল না। কিন্ত আইলার প্রলয়ে সুপেয় পানির সবগুলো আঁধার লবণ পানিতে ডুবে যায়। সেগুলো থেকে এখন আর লবণ পানি সরানো যাচ্ছে না। ফলে মিঠা পানির সংকট দিন দিন বাড়ছে।
‘জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে সুপেয় পানির সন্ধানে’ শীর্ষক প্রতিবেদনে পানি কমিটি বলছে, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল এলাকায় লবণাক্ততার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলাধারের বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ এলাকার অবস্থান ব-দ্বীপের নিম্নাংশ। ফলে নদী বাহিত পলির আধিক্য বেশি। এ কারণে ভূগর্ভে জলাধারের জন্য উপযুক্ত মোটা দানার বালু বা পলির স্তর খুব কম পাওয়া যায়। আর পলির স্তর পাওয়া গেলেও এই বালুর স্তরের পুরুত্ব খুবই কম। আর কোথাও কোথাও এই বালুর স্তরের ভূমি থেকে অনেক গভীরে। সেখান থেকে মিষ্টি পানি উত্তোলন অত্যন্ত দুরূহ।
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, তালা, দেবহাটা, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, মংলা, রামপাল, চিতলমারী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ও শরণখোলা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পানি সংকট আছে। এই এলাকার প্রায় ৫০ লাখ মানুষ কমবেশি খাবার পানির সংকটে রয়েছে। এক কলস পানি সংগ্রহের জন্য মহিলা ও শিশুরা ছুটে যায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। কোনো কোনো গ্রামে মিষ্টি পানির আধার বলতে আছে ২ থেকে ১টি পুকুর। তবে অধিকাংশ গ্রামে পুকুরও নেই।
পানি কমিটি পর্যবেক্ষণে, বাংলাদেশের গভীর নলকূপগুলো সাধারণত ৩০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩০০ থেকে ৪০০ ফুটের মধ্যে গভীর নলকূপ বসানো যায়। কিন্তু দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় এই নলকূপের গভীরতা ৭০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসকল নলকূপের পানি তূলনামূলক কম লবণাক্ত এবং আর্সেনিকমুক্ত। তবে পলি মাটির আধিক্য, পাথরের উপস্থিতি এবং অধিক লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় সব এলাকার গভীর নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হয় না।
কয়রা উপজেলায় মহারজপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ, এলাকায় পানির ফেরীওয়ালা নামে পরিচিত। কারণ সুপেয় পানির সংকটাপন্ন এই এলাকায় তিনি ভ্যানে করে বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ করেন। আজিজের দেখা দেখি আরও অনেকেই এখন দূর দূরন্ত থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহ করে গ্রাহকের বাড়ি পৌছেদেয়াকে পেশা হিসেবে নিয়েছে।
পানি সরবরাহকারী আব্দুল আজিজ জানান, খাবার পানির জন্য আমরা বর্ষাকালের উপর নির্ভরশীল। আমরা প্রার্থনা করি বর্ষাকাল যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। বর্ষাকালের ৩-৪ মাস আমরা ভালো পানি পাই। বাকি সময়টুকু খাবার পানির তীব্র সংকট থাকে।
একই কথা দাকোপ উপজেলার গাবুরা গ্রামের গৃহিণী সালেহা খাতুনের। তিনি বলেন, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পানির আধারগুলো আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ফলে পানির জন্য আমাদের টিকে থাকার লড়াই আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।
দাকোপ উপজেলার কালাবগি ঝুলন্ত গ্রামের বাসিন্দা সুফিয়া বেগম বলেন, আগে আমরা এলাকা থেকেই খাবার পানি সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় দাকোপ উপজেলা সদর থেকে নৌপথে। ট্রলারে করে ড্রাম ভরে পানি আনা হয়।
খুলনা ও সাতক্ষীরা উপকূলীয় এলাকায় ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রায় ৫ বছর এলাকাটি ছিল পানির নিচে। সে সময় খাবার পানির সব আধার নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে ২/৩ কলসি পানি দিয়ে এই এলাকার মানুষের দিনের গৃহস্থলির সব কাজ শেষ করতে হয়। এটুকু পানি সংগ্রহ করতে অনেকের ৩ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় হয়। উপকূলীয় গ্রামগুলোর বাসিন্দারা এভাবেই পানির জন্য লড়াই করছেন বছরের পর বছর। আর এই লড়াইয়ের অগ্রভাগে থাকেন নারী।
কয়রা উন্নয়ন উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: ইমতিয়াজ উদ্দিন এ বিষয়ে বলেন, আমরা পানির মধ্যে বসবাস করি। ঘরের সবদিকে পানি। অথচ খাবারের পানির জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হয়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড় আইলার রেশ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি উপকূলীয় জেলার ৬৪টি উপজেলার প্রায় ৫০ লাখ দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বড় অংশ বয়ে চলেছে। নেপথ্য কারণ হিসেবে তিনটি সমস্যাকে দায়ী করেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলো হচ্ছে: ভূ-প্রাকৃতিক, মানবগৃষ্ট কারণ ও সরকারের সদিচ্ছার অভাব। এ অঞ্চলের মাটিতে বর্তমানে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৬-১৫.৯ পিপিটি; অথচ মাটির সহনীয় মাত্রা ০.৪-১.৮ পিপিটি। লবণাক্ততার কারণে গাছপালার পরিমাণও আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। পুকুরে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মাছসহ জলজ প্রাণীও মারা যাচ্ছে।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মাইনর ইরিগেশন ইনফরমেশন সার্ভিস ইউনিট পরিচালিত দক্ষিণাঞ্চলের ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশ পূর্বাভাস প্রদান’ শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ভূগর্ভস্থ পানিতে বঙ্গোপসাগর থেকে লবণ পানি এসে মিশছে। ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী, নিরাপদ উৎস থেকে পানি সংগ্রহের সুযোগ নেই এমন ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দেশে বর্তমানে প্রায় তিন কোটি মানুষ নিরাপদ পানি সুবিধার বাইরে। যার বেশিরভাগই বাস করে উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে।
বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভাসড স্টাডিজ (বিসিএএস)-এর নির্বাহী পরিচালক ক্লাইমেট চেঞ্জ এক্সপার্ট ড. আতিক রহমান বলেন, বাংলাদেশকে বলা হয় গ্রাউন্ড জিরো অব ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভবত বাংলাদেশই হবে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল একদম সমতল। এতটাই সমতল যে, এক মিটার পানি বাড়লে ১৭ ভাগ ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।